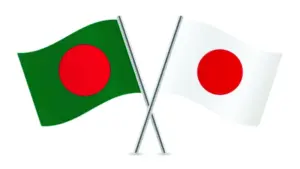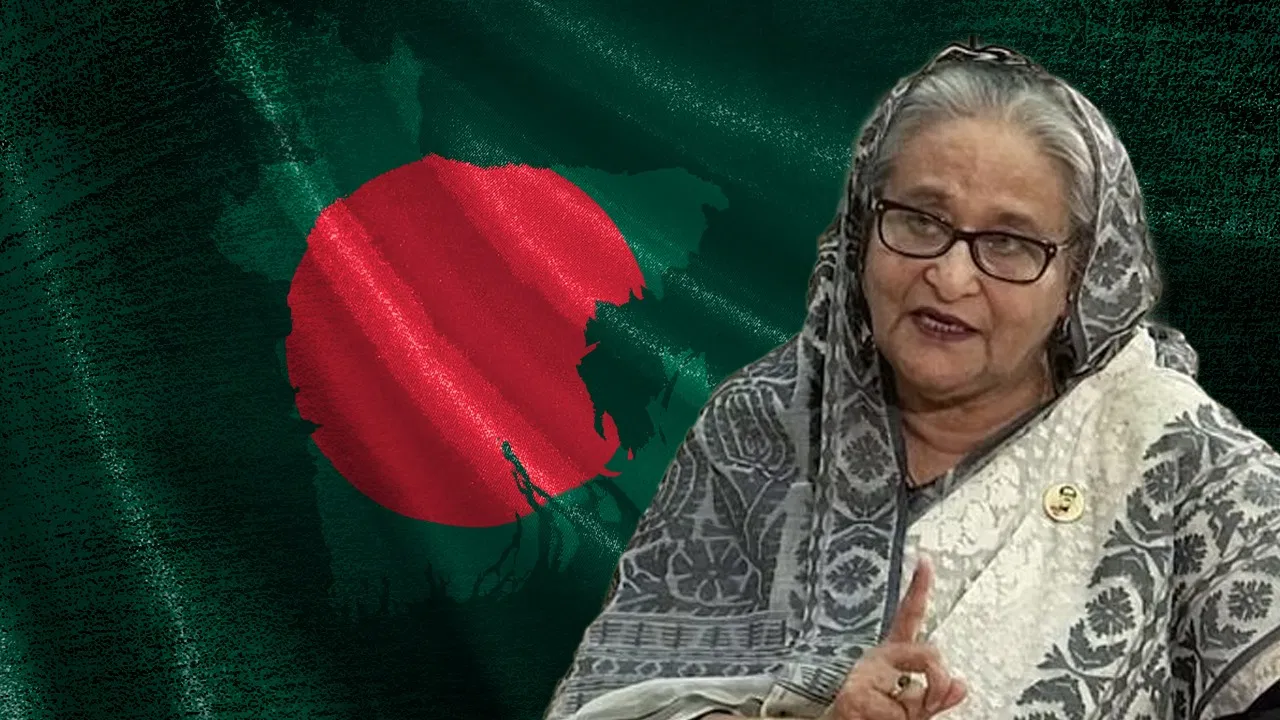আমাদের সমাজে শিক্ষার্থীকে “মানুষ” হিসেবে দেখা হয় না, বরং দেখা হয় “নম্বর-তোলার মেশিন” হিসেবে। মনে হয়, সে যেন ছোট্ট একটা এটিএম বুথ, কার্ড ঢোকালে রেজাল্ট বের হবে। নম্বর কম হলে মেশিনটা নষ্ট, ফেলে দাও। পরীক্ষায় খারাপ করার অপরাধে টিসি, মানে স্কুল থেকে বিদায়, কিংবা অভিভাবকদের ডেকে এনে তাদের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের অপমান! এক ধাক্কায় একজন কিশোরের আত্মমর্যাদা, স্বপ্ন, মানুষ হিসেবে তার সম্মান, সবই ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়।
আমরা যে ছেলেটির গল্প জানি, সে পরীক্ষায় ফেল করেছিল, ক্লাসে অনিয়মিত ছিল। আমাদের তথাকথিত জ্ঞানের দৌড়ে সে পিছিয়ে পড়েছিল, তাই তাকে “টিসি” দেওয়া হয়েছিল। এই দেশের স্কুলের দরজায় যেন লেখা: “ভালো না পড়লে, বের হয়ে যাও”। কিন্তু দরজা পেরিয়ে সে গেছে অন্য এক গন্তব্যে, না ফেরার দেশে। আত্মহত্যা ছিল তার শেষ প্রতিবাদ। স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, অভিভাবক বা আমরা কি আদৌ ভেবে দেখেছি, মরে গিয়ে কী পরিমাণ ঘৃণার থুথু দিয়ে গেছে ছেলেটি আমাদের মুখমণ্ডলে?
শিক্ষার্থীর ভুল করা কি স্বাভাবিক নয়?
বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। ছোট্ট একটা ছেলে যদি পরীক্ষায় ফেল করে, সেটা কি বিশ্বসংসারের পতন? শেয়ার বাজারের ধস, নাকি বড় ধরনের কোনো ভূমিকম্প, মানব সভ্যতার বিনাশ? আমাদের সমাজের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়, হ্যাঁ, এ যেন মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ। অথচ সত্যিটা হলো, ফেল করা মানে বাচ্চাটা অযোগ্য নয়, বরং শেখার পথে একটা হোঁচট খাওয়া। সে শেখার প্রক্রিয়ায় আছে, সে ভুল করবেই।
ভুল করা মানেই শেখা, এই সহজ সত্য আমরা ভুলে যাই। একটা বাচ্চা যখন হাঁটতে শেখে, সে একদিনেই হাঁটতে পারে না। প্রথমে টলোমলো, তারপর ধপ করে পড়ে যায়। কখনো কপালে চোট লাগে, কখনো হাঁটুতে রক্ত পড়ে। তখন কি মা-বাবা রেগে গিয়ে বলেন, “তুমি হাঁটতে পারো না, তাই তোমাকে আর দরকার নেই”? না, বরং তখন পুরো বাড়ি আনন্দে ভরে ওঠে, “দেখো, বাবু হাঁটতে চেষ্টা করছে!” মা-বাবা হাসে, শিশুটাকে কোলে তুলে নেয়, সান্ত্বনা দেয়, আবার নামিয়ে দেয়, “চেষ্টা চালিয়ে যাও।”
তাহলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কেন এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না? কেন স্কুলে সেই হাসিটুকু নেই? সেখানে তো উল্টো নিয়ম, একবার ফেল করলে মানে তুমি অযোগ্য, একবার অনিয়মিত হলে মানে তুমি শৃঙ্খলাভ্রষ্ট। শিশুটিকে কোলে তুলে নেওয়ার পরিবর্তে দেওয়া হয় টিসি। যেন প্রতিষ্ঠান বলছে, “তুমি আর আমাদের দরকার নেই।” আপনাদের জরুরি একটা তথ্য দিই- কোনো ছেলে বা মেয়ে যদি স্কুলে যেতে চায় না, এর দায় কিন্তু স্কুলের। অর্থাৎ স্কুল তার বা তাদের জন্য আকর্ষণীয় নয়, ভয়ের জায়গা। শেখার স্থান হবে আনন্দের, কোনো ভয় বা আতঙ্কের স্থান নয়।
এখানেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মানবিক ঘাটতি। শেখা যদি একটি প্রক্রিয়া হয়, তবে ফেল করা হলো সেই প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ। কিন্তু আমরা ফেলকে দেখি অপরাধ হিসেবে। বাচ্চারা তখন শিখে যায়, “আমি ভুল করলে আমাকে আর ভালোবাসা হবে না।” এই ধারণাই ধীরে ধীরে ভয়, হীনমন্যতা আর হতাশায় পরিণত হয়।
স্কুল যদি পরিবার হতো, তাহলে শিক্ষকরা সেই প্রথম পদক্ষেপে হেসে উঠতেন, বাচ্চাকে কোলে তুলে নিতেন, বলতেন- “কোনো সমস্যা নেই, আবার চেষ্টা করো।” কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্কুল আজ “সংখ্যা আর শৃঙ্খলার কারখানা।” সেখানে হাসির জায়গা নেই, আছে শুধু নম্বরের বিচার আর শাস্তি, হুকুম।
অভিভাবকরা কি আমাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করছি?
মায়ের চোখে ছেলে সবসময়েই “বাবু”, যত বড়ই হোক না কেন। বাবু যদি চা খাওয়ার সময় কাপ ভেঙে ফেলে, মা হাসতে হাসতে বলেন, “আহা, আমার বাবুটা কেমন অমনোযোগী!” কিন্তু পরীক্ষার খাতায় লাল কালি ঢুকলেই সেই বাবুটি আর বাবু থাকে না, হয়ে যায় “অপরাধী।” তখন মা-বাবার কণ্ঠ বদলে যায়: “তুমি কী করছো সারাদিন? এত টাকা খরচ করলাম পড়াশোনায়, আর তুমি ফেল?”
আমরা খুব সহজে ধরে নিই, রেজাল্ট খারাপ মানে ছাত্র অলস বা অমনোযোগী। অথচ এর আড়ালে থাকতে পারে অসংখ্য অদৃশ্য চাপ। হয়তো ঘরে প্রতিদিন ঝগড়া হয়, বাবা-মায়ের কথার লড়াইয়ের শব্দে সে ঘুমোতে পারে না। হয়তো অর্থকষ্ট, টিউশনি দেওয়া সম্ভব হয়নি, বই কেনা হয়নি, প্রাইভেট পড়া হয়নি। আবার হয়তো তার ভেতরেই একাকিত্ব জমে উঠেছে, বন্ধুহীনতা, অপমান, বা কারও সঙ্গে নিজের কষ্ট ভাগ করে নিতে না পারা।
শিশুরা যখন নিদ্রাহীন হয়, হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়, আগে যেটা ভালো লাগত সেটাতে আগ্রহ হারায়, সেগুলো আসলে সংকেত। তারা তখন মুখে না বললেও সাহায্য চাইছে। কিন্তু আমাদের চোখ শুধু খাতার নম্বরে আটকে থাকে। আমরা শুনি না তাদের মনের আওয়াজ।
ঠিক তখনই যদি অভিভাবক বলেন, “আরো পড়ো, তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে”, তাহলে কথাটা শুধু উপদেশ নয়, চাপের ভারী দরজা খুলে দেয়। সেই দরজার অপর পাশে আছে অন্ধকার, আত্মহত্যার দরজা।
মজার বিষয় হলো, আমরা বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রাণপাত করি, ভালো স্কুল, কোচিং, খাতা-কলম, সব কিছুর ব্যবস্থা করি। কিন্তু যখন সেই ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে দরকারি জিনিস, মানসিক সমর্থন, সেটা দিতে যাই না। যেন আমাদের কাছে নম্বরই সব, সন্তানের হাসিমুখ তুচ্ছ।
শিক্ষক ও স্কুল কি দায়িত্ব পালন করছে?
শিক্ষককে আমরা বলি “দ্বিতীয় অভিভাবক।” অভিভাবক যেমন সন্তানকে শুধু খাওয়ান না, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ভুল করলে শাসন করলেও পরে কোলে তুলে নেন, শিক্ষকেরও তো তাই করার কথা। কিন্তু আজকাল শিক্ষকরা অনেকটা প্রশাসনিক কেরানির মতো হয়ে গেছেন। নিয়ম মানো, ইউনিফর্ম পরো, সময়মতো ক্লাসে ঢুকো, নাহলে “তুমি খারাপ ছাত্র।”
অথচ ভাবুন তো, শিক্ষক যদি একদিন ক্লাসে ঢুকে কড়া গলায় রোল নম্বর না ডেকে শুধু জিজ্ঞেস করতেন, “তুমি ভালো আছো তো?” তখন সেই প্রশ্নটাই হতো একধরনের ওষুধ। হয়তো কোনো ছাত্র হেসে ফেলত, কেউ হয়তো থেমে যেত, আবার কেউ ভেতরে ভেতরে ভাঙা বুকটা একটু শক্তি পেত।
কোনো ছাত্রকে টিসি দেওয়ার আগে কি একবারও জিজ্ঞেস করা হয়েছে, “তুমি কেন অনিয়মিত?” হয়তো পড়ার চাপে সে স্কুলের প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছে, হয়তো সে বাড়িতে মায়ের অসুখ দেখছে, হয়তো বাবা বিদেশে, একা লাগে, হয়তো টিউশনের টাকা জোগাড় হয়নি। কিন্তু আমাদের নিয়মে এসব খোঁজার জায়গা নেই। নিয়ম হলো, সমস্যা থাকলে সমস্যা দূর করো। আর সমস্যা দূর করার মানে হলো ছাত্রটাকেই সরিয়ে দাও। কোনো ছাত্রকে বকা না দিয়ে অবশ্যই তাকে কাউন্সেলিং করা উচিত। আপনার স্কুলে কি ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিং কর্নার আছে?
কিন্তু স্কুল যদি সত্যি “শিক্ষালয়” হতো, তাহলে সেখানে শুধু গণিত আর ইংরেজি পড়ানো হতো না, পড়ানো হতো ছাত্রছাত্রীদের মানসিক যত্ন কিভাবে নিতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা শিখত, ভুল করলেও পৃথিবী ভেঙে পড়ে না। স্কুলে থাকত কাউন্সেলর, যার সঙ্গে বসে বলা যেত, “স্যার, আমার ঘুম হয় না,” বা “ম্যাডাম, আমি পড়তে বসলে মাথা ধরে।” “স্যার আমার পড়তে ভালো লাগে না।” শিক্ষকরা জানাতেন, সহানুভূতি কোনো দয়া নয়, বরং শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
মনে রাখবেন, শিক্ষা কেবল অঙ্কের হিসাব মেলানো নয়, এটা জীবনের হিসাব বোঝা। আর যদি জীবনটাই বাঁচানো না যায়, তবে সেই শিক্ষার মানে কোথায়? আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনকে কেবল শিশুর জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে, শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং অভিভাবকদের জন্য সহজলভ্য করা উচিত। কারণ সন্তানকে বড় করার দায়িত্ব একা শিশুর নয়, বরং পরিবার, স্কুল আর সমাজ, সবাই মিলে এই দায়িত্ব ভাগ করে নেয়।
সমাজ ও নীতি-নির্ধারকদের ভূমিকা কি?
আমাদের শিক্ষানীতি এখনো পরীক্ষার খাতার চারপাশে ঘুরপাক খায়। বোর্ড পরীক্ষা, জিপিএ, গ্রেড, এসবই যেন শিক্ষার চূড়ান্ত মাপকাঠি। প্রশ্ন হলো, শিক্ষানীতি যদি শুধু পাশ-ফেলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তবে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যকে কোথায় রাখব? মানসিক চাপ, ভয়, উদ্বেগ, একাকিত্ব, এসবের কোনো অধ্যায় নেই আমাদের নীতিমালায়।
মন্ত্রণালয়ে অনেক কাগজপত্র আছে, পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন, সিলেবাস পরিবর্তন, সবকিছু নিয়েই কাজ হয়। কিন্তু “শিক্ষার্থীর কাউন্সেলিং” নিয়ে কোনো নীতি নেই। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের কোনো উদ্যোগ নেই। যেন মনের দাম শূন্য। অথচ সেই মনটাই সবচেয়ে মূল্যবান। একজন ছাত্রের মন যদি ভেঙে যায়, যদি বিক্ষিপ্ত থাকে, সে আর বই ধরতে পারবে না, ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারবে না, ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারবে না। শিক্ষা তখন রয়ে যায় নিছক কাগজে-কলমে, কিন্তু জীবন হয়ে পড়ে শূন্য।
টিসি?
“টিসি”, এই শব্দটা কেবল স্থানান্তরের কাগজ নয়। এর ভেতরে লুকিয়ে থাকে অপমানের বোঝা। শিক্ষক বা স্কুল যখন বলে “তোমাকে টিসি দেওয়া হলো,” তখন আসলে শুধু স্কুল থেকে সরানো হয় না, সরিয়ে দেওয়া হয় বন্ধুদের দল থেকে, শ্রেণিকক্ষের হাসি থেকে, সমাজের চোখে স্বাভাবিকতার জায়গা থেকে। টিসি হয়ে দাঁড়ায় একধরনের আইনি ও সামাজিক লাঞ্ছনা।
এই শব্দের ভেতরে এক ধরনের নির্মমতা লুকিয়ে আছে। যেন বলা হচ্ছে, “তুমি ব্যর্থ, তাই তুমি অযোগ্য।” অথচ বাস্তবে, টিসি হতে পারত একটি স্বাভাবিক কাগজ, যেখানে শুধু লেখা থাকবে, ছাত্রটি এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে। এতে কোনো শাস্তি নেই, কোনো অপমান নেই, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতা।
আত্মহত্যা?
আচ্ছা, আমরা কি মনে করি আত্মহত্যা হঠাৎ করে ঘটে যায়? একটি ছেলে বা মেয়ে এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়? নাকি তাকে তিলে তিলে এই পথে ঠেলে দেওয়া হয়? বাস্তবে, আত্মহত্যা ধাপে ধাপে তৈরি হওয়া একটি ধ্বংসপ্রকল্প। লজ্জা, একাকিত্ব, আত্মমর্যাদাহানি, প্রত্যাশার বোঝা, এসব মিলিয়ে একটা সেতুর মতো গড়ে ওঠে, যেখানে প্রত্যেকটি আঘাত হলো সেই সেতুকে দৃঢ় করার একটি ইট। মা, বাবা, সমাজ, স্কুল, কলেজ, শিক্ষক, সবাই মিলে আমরা তাকে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিতে বাধ্য করি। ছোট একটা প্রশ্ন রেখে যাই, নিজেকে কখনো একবারও খুনি মনে হয়নি?
কাল্পনিকভাবে ভাবুন: কোনো ছোট্ট লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছে একজন ছাত্র, পেছনে স্কুল, সামনের দিকে ভবিষ্যৎ। প্রতিটি কণ্ঠস্বর, শিক্ষকের দৃষ্টি, বাবার হতাশা, সহপাঠীর বিদ্রূপ, হলো একটি শব্দ, একটি অবচেতন চাপ। যখন এত শব্দ একসঙ্গে বাড়ে, ছাত্রটা কানে কানে শোনে, “তুমি এখানে টিকে থাকতে পারবে না।” আর সেই অনুভূতির সঙ্গে লেগে যায় এক ভয়: “আমার জায়গা কোথায়?”, এ প্রশ্নটা তার অজান্তেই গিলে নেয় তার স্বপ্নগুলো।
লজ্জা, সে এক কঠিন অনুভূতি। লজ্জা যখন চারপাশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন মানুষ সবকিছু লুকাতে চায়। সে লুকায় নিজের ভুল, লুকায় নিজের হতাশা, লুকায় কাঁদার সময়। একাকিত্ব, ওর সঙ্গী হয়ে বসে। একাকিত্ব মানে কোনো কণ্ঠস্বর নেই, কোনো অনুপ্রেরণা নেই, কেউ নেই যে বলবে, “ঠিক আছে, চলো আবার চেষ্টা করো।” আত্মমর্যাদাহানি মানে নিজের চোখে নিজের কদর হারানো, যে মানুষটি কখনোই “বাবু” ছিল, আজ সে নিজেকেই অপরাধী মনে করে। প্রত্যাশার বোঝা, এটাই সবচেয়ে জোরালো; যখন পরিবার, শিক্ষক, সমাজ, সবাই মিলেই বলে, “এটা তোমার শেষ সুযোগ,” তখন সে বোঝা নেওয়ার মতো শক্ত থাকে না।
“টিসি” কেবল কাগজ নয়; কাগজের পেছনে রয়েছে একটি বিবৃতি, একটি সামাজিক সিদ্ধান্ত: “তুমি আমাদের সিস্টেমের অংশ হতে পারছ না।” এই বিবৃতি ছাত্রের মুখে নয়, হৃদয়ে খোদাই করে, একটা ভুলকে করোনার মতো ছড়িয়ে দেয়, আশেপাশে মানুষের আচরণে অনুকরণ করে। যখন স্কুল থেকে অর্থাৎ জীবনের এক নিরাপদ স্থান থেকে নিজেকে বিতাড়িত মনে হয়, তখন সে শিশুটি আর কোথায় যাবে? তার পা কাঁপে, সে গৃহহীন মনে করে, এমন এক পরিস্থিতিতে অনাহূত অন্ধকারই তাকে কাছে টানে।
এখানে আমি লজ্জা, একাকিত্ব, প্রত্যাশা, এই তিনটি ‘ধারণাগত কোলাহল’কে আলাদা করে বলতে চাই: লজ্জা মানুষের আত্মসম্মানকে খোলে; একাকিত্ব সামাজিক সমর্থন কেটে নেয়; প্রত্যাশা মানুষের সম্ভাব্যতা-ঘরটাকে সংকুচিত করে। তিনটি একসাথে হলে, একজন মানুষের ভেতরের সহনশীলতা ক্ষয় হয়, তাই সে মনে করে শুধু ‘অপমৃত্যু’ একটাই রাস্তা বাকি।
আত্মহত্যা কখনোই সমাধানের পথ নয়; একে প্রতিরোধ করা যায়, যখন আমরা সমাজ, স্কুল ও পরিবার হিসেবে শিখব, একটা ভুলের জন্য কাউকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া মানবিক নয়। ছোটখাটো কোমলতা, একটি সময়মতো প্রশ্ন, “তুমি ঠিক আছো তো?”, এগুলো অনেক সময় সেই সেতুর ভেঙে পড়া থামাতে পারে। আমাদের দায়িত্ব হলো সেই কৃত্রিম, নির্মম খুঁটিগুলো তুলে ফেলা, পরে দেখা যাবে, অনেক ছেলে-মেয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়াতে পারছে, আর সেসব ছোট পরিবর্তন একদিন বড় পরিবর্তনে পরিণত হয়।
একটি ভিন্ন পৃথিবীর স্বপ্ন
“আমাদের দেশে বাচ্চারা পুতুল খেলার সময়েই পরীক্ষার ভয় শিখে ফেলে”- রোগটা কতটা গভীরে একবার ভেবে দেখুন। পুতুল খেলার মাঝে শিশু যে নিষ্পাপ খোশমেজাজ, কল্পনা আর নিশ্চিন্ততা পায়, সেখানে আমরা ছোট থেকেই ঢুকিয়ে দিই দরাজ কণ্ঠ: “পরীক্ষা চিন্তা মাথায় নেই? শুধু খেলাধুলা!” পুতুলের হাতে কাটা চুলের কাঁথা হঠাৎ পরিমাপ-ভিত্তিক হয়ে আসে, কত মিনিটে রুটিন শেষ করতে হবে, কোন খেলায় পয়েন্ট কত, সব কিছুকে নম্বরে ভাগ করে ফেলি। শিশুর খেলার ঘরেই আমরা নম্বর-অভ্যাস বপন করি; ফলে খেলতেই শুরু হয়ে যায় ভয়ের সমাবেশ।
পরীক্ষার খাতা কাগজ, কিন্তু আমরা তা জীবনের মাপ হিসেবে মূর্ত করে তুলি। আমরা কাগজটাকে দেবতুল্য করে বসাই, যে দেবতা তার কাছে সন্তানের মর্যাদা, পরিবারের গৌরব, ভবিষ্যতের মানচিত্র সব ঢেলে রাখবে। ফলে যখন কাগজটা লাল করে দেয়, মনে হয় দেবতাই অভিশপ্ত হয়ে গেল। অথচ বাস্তবে খাতা কেবল তথ্য, কোন বিষয়ে দুর্বলতা, কোন অংশে আরও অনুশীলন দরকার, এটুকুই। জীবনের সঙ্গে খাতার সম্পর্কটা যতটা হতে পারে না, আমরা তাকে ঠিক ততটাই করে ফেলি, অতিরঞ্জন করে।
জীবন যদি আমরা ভালোবাসতে শিখতাম, অর্থাৎ জীবনের মূল্য বুঝতে, ক্ষুদ্র ব্যর্থতাকে ক্ষমা করতে, পরাজয়কে শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে, তাহলে কোনো শিশুই তার জীবন শেষ করার মতো অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাত না। ভালোবাসা বলতে কী বোঝায়? এটা কোনো সোনার ব্যাজ বা ডিগ্রি নয়; এটা সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোলে যে একটি হাসি, ক্লাসে একজন শিক্ষক যে বলেন “ভুল করলে ভয় নেই,” একজন অভিভাবক যে বলেন “চেষ্টা করলেই হবে।” ভালোবাসা মানে বিকল্প রাস্তাগুলো খোলা রাখা, রিমিডিয়াল ক্লাস, কাউন্সেলিং, পিয়ার সাপোর্ট, যেগুলো বলে, “তুমি একা নও।”
আর যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সহানুভূতি, ন্যায়বিচার আর সমর্থনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সেটা কোনো কল্পবিজ্ঞানের কথা নয়; এটা বাস্তবিক পরিবর্তন। সহানুভূতি মানে শিক্ষক, প্রশাসন ও অভিভাবক একসাথে বসলেন, খেয়াল রাখলেন কিভাবে একটা শিশুর জীবনচিত্র গড়া হলো; ন্যায়বিচার মানে টিসিকে শাস্তি বানিয়ে ব্যবহার করা নয়, বরং টিসিকে কেবল স্থানান্তরের কাগজে পরিণত করা; সমর্থন মানে সুযোগ দেওয়া, শিক্ষা থেকে বাদ না দিয়ে, বরং যাকে সহায়তার প্রয়োজন, তাকে সাহায্য করা।
এই তিনটি ভিত্তির ওপর দাঁড়ালে “টিসি হাতে নিয়ে গলায় দড়ি খোঁজা”, এমন চিত্রগুলো অচল হয়ে পড়বে। কারণ অপমানের জায়গা থাকবে না; লজ্জা, একাকিত্ব আর প্রত্যাশার ভারও কমবে। যেখানে কারো ভুল করা মানে তার শেষ নয়, সেখানে ছেলে-মেয়েরা ভুল থেকে উঠে দাঁড়াতে শিখবে। আর যে সমাজ শিশুদের শেখায় কিভাবে খেলা করে, কিভাবে পড়ে উঠে দাঁড়ায়, সেই সমাজে হয়তো আর কোনো সন্তানের গলায় দড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না।
শেষে একটু কড়া ভাষায় বলতে চাই: আমরা যদি আজও খাতার লাল দাগকে জীবনের রঙ ধরে রাখি, তাহলে আগামীকাল আমাদেরই সন্তানেরা সেই লাল দাগেই গলায় দড়ি বানাবে। পরিবর্তন করতে হবে দ্রুত, কিন্তু প্রথমে প্রয়োজন দরদমিশ্রিত সাহস: ভাঙতে হবে সংখ্যাপূজার মূর্তি, আর গড়তে হবে এমন এক শিক্ষা যেখানে কাগজ যতই মূল্যবান হোক, মানুষের মন তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।
মনে রাখবেন, ব্যর্থতার দায় সবার! আমরা প্রায়ই বলি, “ছাত্রছাত্রী মনোযোগ দিচ্ছে না, তাই ফল খারাপ।” যেন সব দায় তার মাথাতেই। কিন্তু কি সত্যিই তাই? একজন শিশু যখন শিখতে পারছে না, তখন ব্যর্থতার দায় কেবল তার নয়, এর বড় অংশ আমাদের শিক্ষকদের, অভিভাবকদের এবং অবশ্যই সমাজের।
শিক্ষক যদি কেবল পাঠ্যবই শেষ করাকে নিজের কর্তব্য মনে করেন, আর ছাত্র বুঝছে কিনা সেদিকে খেয়াল না রাখেন, তাহলে অমনোযোগী হওয়ার দায় কতটা ছাত্রের? শিক্ষক যদি কখনো শেখার আনন্দ দেখাতে না পারেন, শুধু নম্বরের ভয় দেখান, তাহলে শিশুটি শেখার প্রেমে পড়বে নাকি ভয়ে কুঁকড়ে যাবে?
অভিভাবকের ক্ষেত্রেও একই কথা। শিশুর ঘরে পড়ার পরিবেশ নেই, ঝগড়া, টানাপোড়েন, অর্থকষ্টে ভরা সংসার, এখানে বাচ্চা মনোযোগ কোথায় পাবে? আবার অনেক সময় অভিভাবকরা কেবল বলেন, “ভালো রেজাল্ট করো,” কিন্তু কীভাবে করবে, কীভাবে সাহায্য পাবে, সেই দিকনির্দেশনা দেন না। তখন শিশুটি ব্যর্থ হলে দায় কেবল কি তার একার?
আর সমাজ? সমাজের অবিরাম তুলনা, “ওর ছেলে তো ফার্স্ট হয়েছে, তুমি পারলে না কেন”, এগুলোই তো শিশুর আত্মবিশ্বাস চূর্ণ করে। যখন প্রত্যেক ভুলকে কলঙ্ক বানানো হয়, তখন ভুল থেকে শেখার পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যায়।
অতএব, ছাত্রছাত্রীদের ব্যর্থতার দায় ভাগ করতে হবে। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শেখাকে আনন্দময় করা, অভিভাবকের দায়িত্ব হলো মানসিক সহায়তা ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা, সমাজের দায়িত্ব হলো ভুলকে শাস্তি নয়, শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা। তখনই অমনোযোগিতা কমবে, শেখা সহজ হবে, আর আমরা একটি মানবিক ও সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব।