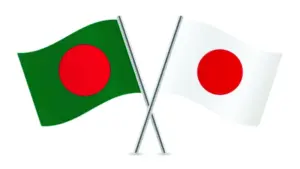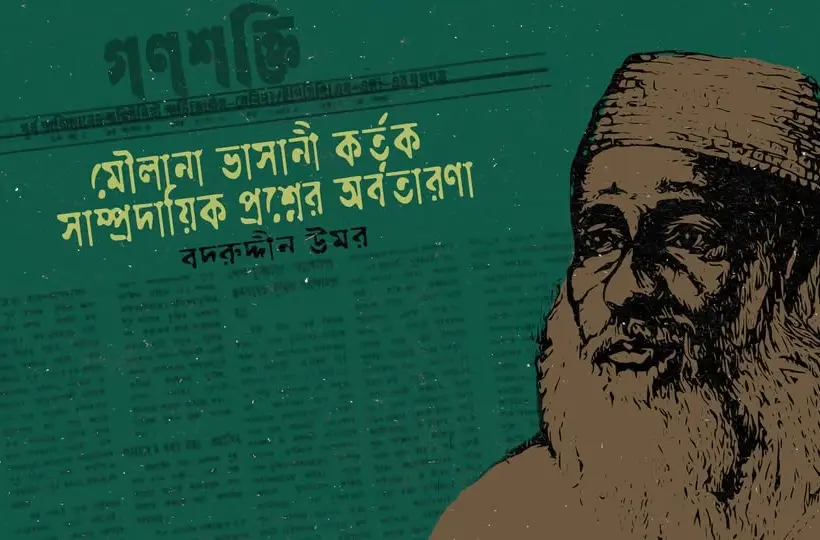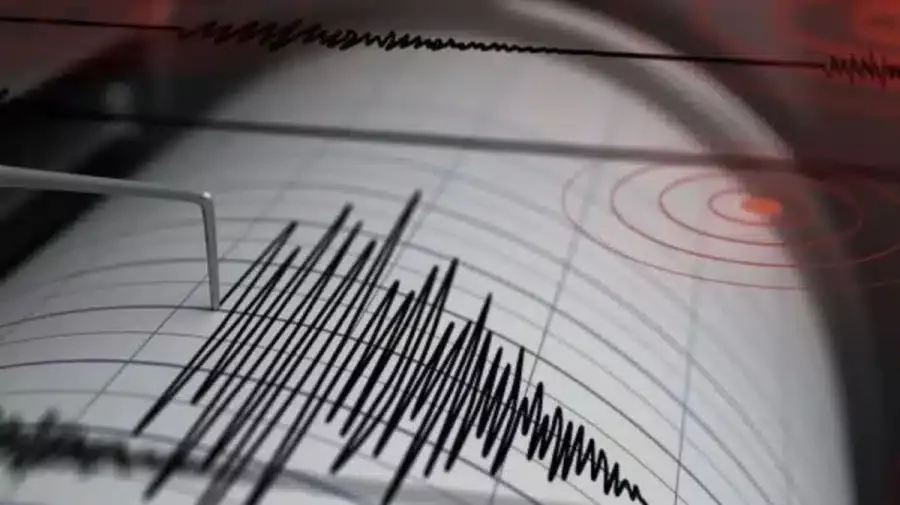পশ্চিম পাকিস্তানের টোবাটেক সিং-এর কৃষক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের সময় মৌলানা ভাসানী তেজগাঁ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সামনে বলেন যে, পূর্ব বাঙলায় হিন্দু বামপন্থী নেতারা তাদের ভক্ত নগণ্য মুসলমান কর্মীদের সাথে নিয়ে ন্যাপ ও কৃষক সমিতিকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, পূর্ব বাঙলার জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ জনই মুসলমান, কাজেই তাদেরকে এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয় (দৈনিক পাকিস্তান ও পাকিস্তান অবজার্ভার- ২২শে মার্চ, ১৯৭০)।
এতদিন যাঁরা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মৌলানা ভাসানীর সাথে একত্রে কাজ করেছেন তাঁরাতো বটেই, এমনকি পূর্ব বাঙলার সংগ্রামী জনগণও যে মৌলানার উক্তিতে লজ্জিত ও বিক্ষুদ্ধ হবেন-তাতে কোন সন্দেহ নেই। বামপন্থী নেতাদেরকে হিন্দু হিসেবে আখ্যায়িত করে মৌলানা ভাসানী যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইছেন, তা মূলতঃ মুসলিমলীগ জামাতে ইসলামীর উদ্দেশ্য থেকে পৃথক নয়, বরং তার পরিপূরক। এ কথা চিন্তা করে আজ মৌলানার উক্তিতে অনেকে যে শুধু লজ্জিত, বিব্রত ও বিক্ষুব্ধ বোধ করছেন তাই নয়, তাঁর বর্তমান রাজনৈতিক চরিত্র এবং এদেশের গণতান্ত্রিক বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কেও আজ ব্যাপকভাবে প্রগতিশীল কর্মী মহলে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।
বামপন্থী রাজনীতির নেতৃত্বে ও কর্মীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেই আছেন। কিন্তু সেটা আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়। কে কোন ধর্মাবলম্বী তার ভিত্তিতে বামপন্থী রাজনীতি কোনদিনই গঠিত হয়নি, এখনো হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। উপরন্তু ধর্মীয় প্রশ্নকে রাজনীতিগতভাবে উত্তীর্ণ হয়েই অন্যান্য দেশের মত পূর্ব বাঙলাতেও গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনীতির প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি। মৌলানা ভাসানী যে এ-সব কথা জানেন না তা নয়। তিনি তা বিলক্ষণ জানেন। তবু কেন তিনি আজ বামপন্থী রাজনীতিক্ষেত্রে এত দায়িত্বহীনতার সাথে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের অবতারণা করলেন? তাঁর এই বক্তব্য কি আকস্মিক না ইচ্ছাকৃত? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে মৌলানার বিগত এক বছরের বক্তব্যসমূহের সাথে এই বক্তব্যকে মিলিয়ে দেখতে হবে।
১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে মৌলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যান। সেখানে কোন কোন মহলের সাথে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সে প্রসঙ্গের কোন অবতারণা না করেও আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, তাঁর সেই সফরকালে তিনি খুব জোরেশোরে ইসলামী সমাজতন্ত্র দাবি করে বেড়ান। এর পূর্ব পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ন্যাপ ও কৃষক সমিতির প্রধান হিসাবে তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলে এসেছেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকলেও সাধারণভাবে জনগণ তাঁর এই প্রচারে সাড়া দেয় এবং কায়েমী স্বার্থ ও তাদের প্রতিভূ জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। এই বিরোধিতা ও আক্রমণের মুখে পড়ে মৌলানা সমাজতন্ত্রের পূর্বে ইসলামী জুড়ে দেন এবং ইসলামী সমাজতন্ত্রের স্লোগান তোলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রের এই বিকৃত বক্তব্য হাজির করলে পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক মহলে এ বিষয়ে বিস্তৃত সমালোচনা শুরু হয়। সফর শেষে তিনি পূর্ব বাঙলায় ফিরে এলে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণও করা হয়। কিন্তু তিনি সে সব ভ্রুক্ষেপ না করে সমাজতন্ত্রকে ছেড়ে ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রচারে পুরোপুরিভাবে নেমে পড়েন।
একথা সকলেরই নিশ্চয় মনে আছে যে, শাহপুরে কৃষক সমাবেশের ঠিক পূর্বে পাবনা থেকে বিবৃতি মারফত মৌলানা ভাসানী ভারতের আহমদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে ৩রা অক্টোবর কালো পতাকা উত্তোলন সভাসমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে এক দিবস পালনের আহ্বান জানান। পূর্ব বাঙলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ইতোমধ্যেই অনেকখানি অবনতি ঘটছিল। মৌলানার বিবৃতির পর সে অবস্থা আরও ঘোরতর আকার ধারণ করে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং প্রদেশের অন্যান্য জায়গায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে পূর্ব বাঙলাবাসীকে রক্ষা করার জন্য কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক নেতাও মৌলানা ভাসানীর দিবস পালনের আহ্বানের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে দফতর সম্পাদক সৈয়দ জাফরের বিবৃতি মারফত কৃষক সমিতির কর্মীবৃন্দকে ঐ দিবস পালন করতে নিষেধ করা হয়। সারা দেশব্যাপী এইভাবে মৌলানার প্রতিবাদ দিবস পালনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে তিনি অবশেষে নিজের আহ্বান প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।
মৌলানা ভাসানীর এই সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা সাধারণ কর্মী মহলে বিস্তৃতভাবে নিন্দিত হলেও তাঁর অন্ধ সমর্থকরা তাঁর এই দিবস পালনের আহ্বানের মধ্যে যথেষ্ট ‘রাজনৈতিক প্রজ্ঞার’ পরিচয় পান এবং মৌলানার ভূমিকাই যে সঠিক একথা বলে বেড়ান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মৌলানা ভাসানীর এই ধরনের সমর্থকরাই শাহপুর ও সন্তোষে কৃষক সমাবেশের ‘অধিনায়ক’ ও ‘পান্ডা’ ব্যক্তি।
পশ্চিম পাকিস্তানের টোবাটেক সিং-এর কৃষক সমাবেশেও মৌলানা ভাসানী অনেক কথাই বলেছেন, অনেক দাবিই উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এগুলির মধ্যে তাঁর মূল কথা এবং মূল দাবি হলো ‘ইসলামী সমাজতন্ত্র’। তিনি সামরিক সরকারের কাছে দাবি করেছেন, ইসলামী সমাজতন্ত্রের সমর্থনে গণভোট অনুষ্ঠানের। এই গণভোট অনুষ্ঠান না করলে অনেক কিছু করবেন বলেও তিনি হুমকি দিয়েছেন। এর ফলে বামপন্থী প্রগতিশীল মহলে আজ স্বভাবতঃই প্রশ্ন জেগেছে, সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ন্যাপ ও কৃষক সমিতির প্রধান হিসাবে তিনি কোন ভিত্তিতে এই দাবি উত্থাপন করলেন?
উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, ঢাকা বিমান বন্দরে ২১শে মার্চ মৌলানা ভাসানী সাংবাদিকদের কাছে যে বিবৃতি দেন তা আকস্মিক অথবা উদ্দেশ্যহীন নয়। বস্তুত বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলেও বিগত এক বছর থেকে তিনি বেশ ভালভাবেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছেন। এবং তাঁর এই ঝোঁকের ফলে তিনি পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছেন।
রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতা মুক্তির মধ্যে দিয়েই পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্বোধন। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পূর্ব বাঙলার জনগণ বহু ত্যাগ ও রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে এদেশের রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে অনেকাংশে মুক্ত করে তাকে আজ প্রতিষ্ঠা করেছেন গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর। যে কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী যদি এই ত্যাগ ও রক্তপাতকে অস্বীকার করে পূর্ব বাঙলার রাজনীতির মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢোকানোর চেষ্টা করেন তাহলে জনগণ নিজেদের শক্তি দিয়েই তার মোকাবেলা করবে। সেই গণশক্তির কাছে কোন ব্যক্তি, দল বা স্বার্থ উদ্ধারকারী গোষ্ঠী দাঁড়াতে পারবে না।
মৌলানা ভাসানীর সাম্প্রদায়িক বক্তব্যসমূহের সাথে ইদানিং শুরু হয়েছে তাঁর গণচীনবিরোধী কথাবার্তা। মুখে তিনি পাকিস্তানের সাথে চীনের বন্ধুত্ব রক্ষার কথা সভাসমিতিতে বলে বেড়ালেও হককুল ইবাদ মিশনের বুলেটিনে তিনি গণচীনকে আক্রমণ করেছেন। মৌলানার এই সব বক্তব্যের মধ্যে অনেকে সামঞ্জস্যের অভাব দেখলেও আসল ব্যাপার কিন্তু অন্য রকম। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বক্তব্যসমূহকে খাপছাড়া মনে হলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র একটু লক্ষ্য করলেই সহজে ধরা পড়ে। এই যোগসূত্র জনগণের কাছে এখন পর্যন্ত কিছুটা অস্পষ্ট মনে হলেও অদূর ভবিষ্যতে তা আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়।
[পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস-লেনিন) / ইপিসিপি (এম-এল)-এর মুখপত্র ‘গণশক্তি’-তে ২৯ মার্চ, ১৯৭০ তারিখে এই নিবন্ধটি লিখেন গণশক্তির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বদরুদ্দীন উমর]