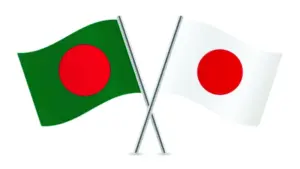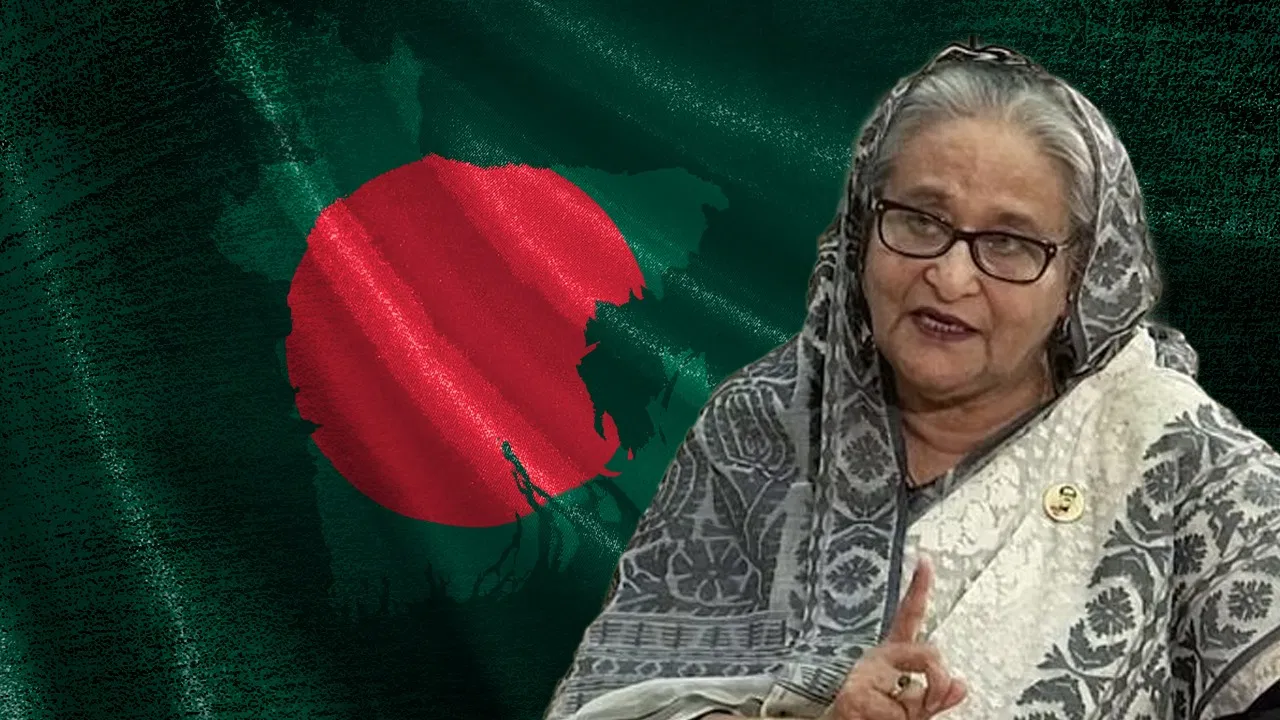অসহিষ্ণুতা যেন বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে মিশে আছে। কেউ কিছু বললেই আমরা ক্ষেপে যাই, ধৈর্যের লেশমাত্র নেই আমাদের আচরণে। রাস্তার পাশে ধাক্কা লাগলে ‘মাফ করবেন’ বলার বদলে গালাগালি, আর সামাজিক মাধ্যমে মতভেদ মানেই চরিত্রহনন, এ যেন নতুন স্বাভাবিকতা।
কোনো কথা শোনার আগেই উত্তর তৈরি, যুক্তির বদলে উত্তেজনা, প্রশ্ন করলেই উত্তেজনা। আমরা সবাই যেন অদৃশ্য এক রণক্ষেত্রে আছি, যেখানে সামান্য শব্দও হয়ে যায় যুদ্ধের ঘোষণা। এই অবস্থায় সমাজ আর রাষ্ট্র, দুটোই পরিণত হচ্ছে বারুদের স্তূপে, যেখানে এক চিলতে আগুনেই হতে পারে সর্বনাশ।
চায়ের দোকানে চা দিতে দেরি করায় খুন। ব্যাংকের কাউন্টার বা টিকেট কাউন্টারে অধৈর্য মানুষের চিৎকার। রাস্তায় সিএনজি বা রিকশা চালকের মারামারি। সোশ্যাল মিডিয়ায় আনসোশ্যাল কন্টেন্ট! অশ্লীল মন্তব্য। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত সামাজিক চাপ, মনস্তাত্ত্বিক বিষক্রিয়া ও কাঠামোগত সংকটের বহিঃপ্রকাশ।
আলোচনার গভীরে প্রবেশের পুর্বে আগে জেনে নিতে হবে সহিষ্ণুতা এবং অসহিষ্ণুতা শব্দে সংজ্ঞা ও অর্থ কি। এই দুটি শব্দ মানবিক আচরণের দুই বিপরীত মেরু।
সহিষ্ণুতা (Tolerance): অন্যের মত, বিশ্বাস, আচরণ বা পার্থক্যকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ বা সহ্য করার মানসিকতা। বাংলা প্রতিশব্দসমূহ: সহনশীলতা, ধৈর্য, মরমি মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা, সহনযোগ্যতা, সহনক্ষমতা, সহনাগ্রতা, সহাবস্থানের মনোভাব।
ইংরেজি প্রতিশব্দসমূহ: Tolerance, Patience, Forbearance, Acceptance, Open-mindedness, Broad-mindedness, Understanding, Endurance (contextual)
অসহিষ্ণুতা (Intolerance): অন্যের মত, বিশ্বাস, আচরণ বা পার্থক্যকে মেনে না নেওয়া বা সহ্য না করার মানসিকতা।
বাংলা প্রতিশব্দসমূহ: অসহনশীলতা, হিংস্রতা (প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে), অপারগতা, প্রতিকূলতা, সংকীর্ণতা, মতদ্বেষ, পরমতঅসহিষ্ণুতা, আগ্রাসী মনোভাব
ইংরেজি প্রতিশব্দসমূহ: Intolerance, Narrow-mindedness, Bigotry, Prejudice, Inflexibility, Impatience, Close-mindedness, Discrimination (contextual)
চলুন আমরা অনুসন্ধান করি, কেন সমাজ এমন আগ্রাসী হয়ে উঠছে? কোথায় এর শেকড়? এবং কী হতে পারে সমাধান?
চলুন খতিয়ে দেখি, ব্যক্তির ভেতরে জমে থাকা ক্ষোভ কীভাবে সামষ্টিক সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে, পরিবার থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত কোথায় কোথায় ফাঁক তৈরি হচ্ছে, এবং রাষ্ট্র ও রাজনীতি কতটা দায় এড়াতে পারে এই সহিংসতার জন্য। একজন সচেতন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে করি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এবং বাস্তবভিত্তিক সমাধান।
১. অর্থনৈতিক চাপ ও বৈষম্য
আমরা নিজেরা নিজেরা বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি নিয়ে যতই আত্মতৃপ্তিতে ভুগি না কেন, আদতে আমরা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশ। সাথে যুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ভুখন্ডে বিশাল জনসংখ্যা, যাদের বৃহত্তর অংশ আবার আনস্কিল্ড, বেকার। শহরে দালান কোটায় বসবাস করে আমরা যাদের দেখি তারা আদতে মোট জনসংখ্যার খুবই ছোট অংশ। শুনে অবাক হবেন, বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের শীর্ষ ১০% মানুষের হাতে মোট সম্পদের ৪১%। আর নিম্ন আয়ের ২০% মানুষ আদতে দিন আনে দিন খায়, প্রতিদিন টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই বৈষম্য ব্যক্তি পর্যায়ে গভীর হীনম্মন্যতা ও হতাশার জন্ম দেয়।
ঢাকায় বসবাসকারী একজন দরিদ্র যুবকের জীবনে কোনো নিরাপত্তা নেই, না অর্থনৈতিক, না সামাজিক। ফলে ক্ষুদ্র দ্বন্দ্বও তার কাছে “মরলে মরবো” ধরনের এক প্রতিক্রিয়াশীল উত্তেজনায় রূপ নেয়।
২. শিক্ষার গুণগত সংকট
আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা “স্মার্ট ফোনের মেমোরি কার্ডের মতো”, অনেক তথ্য জমা হয়, কিন্তু অনুভব করার বা প্রক্রিয়াজাত করার সময় থাকে না। প্রাথমিকে ভর্তি হার ৯৮% হলেও, ‘সহমর্মিতা’ বা ‘সংঘাত সমাধান’ শেখানোর মতো নৈতিক পাঠ প্রায় অনুপস্থিত।
এডুকেশন ওয়াচ ২০২৩-এর জরিপে জানা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ৬৭% শিক্ষার্থী সংঘাত বা রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রশিক্ষণ পায় না। যারা নৈতিক শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের মধ্যেই নৈতিকতার অভাব। যে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি শিশু বেড়ে উঠছে, সেখানে সমাজই তার নৈতিকতা নষ্ট করে দিচ্ছে।
৩. সামাজিক বন্ধনের ক্ষয়
এক সময় মানুষ একসাথে উঠান বৈঠক করতো, এখন সবাই নিজের স্ক্রিনে বন্দী। ‘সামাজিক পুঁজি’ (social capital), অর্থাৎ পারস্পরিক আস্থা, নির্ভরতা, ও বন্ধনের ভীত নড়ে গেছে।
বিশ্ব মূল্যবোধ জরিপ (WVS, 2022) বলছে, বাংলাদেশে অপরিচিত মানুষের প্রতি আস্থা মাত্র ১৮.৫%।
এটি সমাজে এক গভীর নিরাপত্তাহীনতা এবং রক্ষণাত্মক মানসিকতা সৃষ্টি করছে, যা রূপ নিচ্ছে আগ্রাসনে। স্ম্রণ করে দেখুন, এই সেদিনও নব্বুই দশকে আমাদের মা বাবা আমাদের একা স্কুলে যেতে দিতেন, একা খেলাধূলা করতে দিতেন… আর আজ!!!
৪. মানসিক চাপ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৪ সালের এক গবেষণায় জানা যায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে প্রায় ৫৮% নগরবাসী দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপ বা chronic stress-এ ভুগছে।
এই মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে বহুস্তরীয় বাস্তবতা:
>অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা: মাসের শেষে হাত খালি থাকা, চাকরি হারানোর ভয়, ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়
>যানজট ও নগরজীবনের বিশৃঙ্খলা: প্রতিদিন গড়ে ৩ ঘণ্টারও বেশি সময় ট্র্যাফিকে নষ্ট হওয়া, যা ক্লান্তি ও ক্ষোভ বাড়ায়
>পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কের অবনতি: একাকীত্ব, দাম্পত্য কলহ, অভিভাবক-সন্তান দ্বন্দ্ব
>প্রতিযোগিতার চাপ: সামাজিক ও একাডেমিক সফলতা নিয়ে অতিরিক্ত প্রত্যাশা
>সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতিবাচক কনটেন্ট ও তুলনামূলক মানসিকতা: “সফলদের” কৃত্রিম ঝলক দেখে নিজেকে ব্যর্থ ভাবা
>বিনোদন ও অবসরের অভাব: বিশ্রামহীন, কর্মব্যস্ত জীবনে নিজের জন্য সময় না থাকা
এই প্রতিনিয়ত চাপ ও উদ্বেগ যখন উপযুক্ত উপায়ে প্রশমিত হয় না, তখন তা Frustration-Aggression Theory অনুযায়ী অন্যদের ওপর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বেরিয়ে আসে, সহিংস আচরণ, হঠাৎ রাগ, বা ভাঙচুরের মাধ্যমে। বিশেষ করে যুবসমাজে ইমপালস কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার বেড়ে চলেছে, যেখানে ব্যক্তি কোনো ঘটনা ঘটার মুহূর্তেই হিংস্র বা অনিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া দেখায়, যার পেছনে যুক্তি নয়, কাজ করে অবদমন ও বিস্ফোরণ।
৫. রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও দায়মুক্তির চর্চা
রাজনৈতিক সহিংসতা এখন আর নিন্দার কিছু নয়, বরং অনেকের কাছে তা হয়ে উঠেছে “লিগ্যাসি” বা বংশগত অর্জনের মতো। কেউ যদি কোনো মিছিলে গুলি ছুঁড়েছেন, প্রতিপক্ষের অফিসে আগুন দিয়েছেন, বা কারও মাথা ফাটিয়েছেন, তা যেন তার দলের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ, এবং ভবিষ্যতের পদ-পদবির টিকিট।
এই সহিংসতা যখন প্রশংসিত হয়, তখন তা কেবল অপরাধ থাকে না, পরিণত হয় একটি রাজনৈতিক পুঁজিতে।
Transparency International Bangladesh (2023)-এর তথ্য বলছে, রাজনৈতিক সহিংসতার ৭২% মামলার বিচারই সম্পন্ন হয় না। মানে, যারা অপরাধ করে, তারা বেশিরভাগই শাস্তি পায় না, অথবা মামলা বাতিল, প্রভাব খাটানো, বা রাজনৈতিক রদবদলের সুযোগে পার পেয়ে যায়।
এ অবস্থায় সমাজে জন্ম নেয় এক ভয়ংকর সংস্কৃতি, “দায়মুক্তি” (Impunity)। এর মানে দাঁড়ায়: আপনি অপরাধ করলেও যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হন বা ‘সঠিক পক্ষের লোক’ হন, তাহলে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে না।
এই দায়মুক্তি কেবল অপরাধীদের উৎসাহ দেয় না, এটি পুরো সমাজে একটি বার্তা ছড়িয়ে দেয় যে, আইনের শাসন নয়, শাসকের ইচ্ছাই শেষ কথা। ফলে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা হারায়, আর অপরাধীরা হয়ে ওঠে আরও বেপরোয়া। এভাবেই সহিংসতা ক্রমে ব্যক্তিগত আচরণ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রণালীতে রূপ নেয়।
৬. নগরায়ণ ও জনসংখ্যার চাপ
ঢাকা শহরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩০,০০০+ মানুষ। UNFPA এই ধরনের ‘ক্রাউডিং ইফেক্ট’-কে আগ্রাসনের বড় উৎস বলে চিহ্নিত করেছে। যখন ব্যক্তি পর্যায়ে জায়গা কমে যায়, ব্যক্তিত্বও সংকুচিত হয়ে পড়ে। মানুষ হয়ে ওঠে ছটফটে, রুক্ষ, এবং রাগান্বিত।
৭. মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব
এক সময় মানুষ সহিংসতা দেখে আঁতকে উঠত, এখন তা দেখে ‘শেয়ার’, ‘রিয়্যাক্ট’ আর ‘ট্রেন্ডিং’ বোঝে। সহিংসতার ভিডিও, গালাগালি ভর্তি বিতর্ক, কিংবা একপাক্ষিক ঘৃণামূলক বার্তা, এসব এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দৈনন্দিন কনটেন্টে পরিণত হয়েছে। অনেক তরুণ প্রতিদিনই এসব কনটেন্ট দেখছে, শোনছে, এবং অনুকরণ করছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ৬১% তরুণ বিশ্বাস করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণা ও সহিংস ভাষা তাদের সহিংস আচরণের প্রতি সহনশীল করে তুলছে। ঘৃণার ভাষা, বিভাজনের বার্তা ও প্রতিপক্ষকে হেয় করার প্রবণতা যত বেশি দেখানো হয়, তত বেশি মানুষ এগুলোকে ‘স্বাভাবিক’ ও ‘গ্রহণযোগ্য’ ভাবতে শুরু করে।
এখন সহিংসতা আর শুধু অপরাধ নয়, এটি হয়ে উঠেছে এক ধরনের বিনোদন। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই সমাজে সহিষ্ণুতা দুর্বলতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। যে যত শান্ত, সে তত “ভীতু”; আর যে যত রেগে ওঠে, সে তত “বীর”, এই বিপজ্জনক মানসিকতা গড়ে ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে।
ফলাফল? যুক্তিহীন উত্তেজনা, ঘৃণার বাজারে জনপ্রিয়তা, এবং এক সহিংস সামাজিক মানস গঠনের প্রতিযোগিতা।
এই প্রবণতা রুখতে হলে কেবল কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ নয়, গড়ে তুলতে হবে মিডিয়া লিটারেসি, যেন তরুণেরা জানে কীভাবে চিনে নিতে হয় সত্য, কীভাবে প্রতিরোধ করতে হয় ঘৃণাকে।
৮. আচরণগত পর্যালোচনা: সহিংসতার অন্তর্নিহিত মানসিক চালিকা শক্তি
সহিংসতা কেবল সামাজিক বা রাজনৈতিক প্ররোচনার ফল নয়, এটি অনেক সময় একটি আচরণগত বা স্নায়ুবৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেও দেখা দেয়। মানুষ যখন দীর্ঘ সময় ধরে মানসিক চাপে থাকে, ন্যায্যতা বঞ্চিত হয়, অথবা উত্তেজক পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তখন তার আচরণে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা সরাসরি সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। নিচে এমন কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো,
১. IED (Intermittent Explosive Disorder)
সংজ্ঞা: এটি একটি মানসিক স্বাস্থ্যগত অবস্থা, যেখানে ব্যক্তি প্রায়শই হঠাৎ করে অতি তীব্র রাগে ফেটে পড়ে এবং সহিংস আচরণ করে, যা পরিস্থিতির তুলনায় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।
উদাহরণ: কেউ যদি চায়ের দোকানে একটু দেরিতে চা পেলে গালাগালি করে বা চেয়ার ছুঁড়ে মারে, তা IED-এর লক্ষণ হতে পারে।
২. লো ইমপালস কন্ট্রোল (Low Impulse Control)
সংজ্ঞা: এই অবস্থা বোঝায়, যখন কেউ তার আবেগ বা আচরণ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়, বিশেষত রাগ বা হতাশার মুহূর্তে।
স্নায়ুবিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা: এই সমস্যা সাধারণত মস্তিষ্কের Prefrontal Cortex নামক অংশের অপ্রতিসম বিকাশ বা কার্যকারিতার দুর্বলতার কারণে হয়। এই অংশটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক আচরণ পরিচালনার জন্য দায়ী।
ফলাফল: এই ব্যক্তিরা ছোট ঘটনাতেও বড় প্রতিক্রিয়া দেখায়, কখনও নিজেই উপলব্ধি না করেই।
৩. Collective Aggression (সমষ্টিগত আগ্রাসন)
সংজ্ঞা: এটি এমন এক আচরণ যেখানে ব্যক্তি তার নিজস্ব রাগ বা বিরক্তিকে এককভাবে প্রকাশ না করে, বরং দলীয় উস্কানিতে আরো তীব্র ও সহিংস হয়ে ওঠে।
তত্ত্ব: Group Polarization Theory (Moscovici & Zavalloni, 1969) অনুযায়ী, যখন মানুষ সমমনা একটি গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে, তখন তারা নিজেদের অবস্থান আরও চরম দিকে নিয়ে যায়।
উদাহরণ: রাজনৈতিক মিছিলে একজন মানুষ হয়তো কখনো পাথর ছুঁড়তেন না, কিন্তু পুরো দল doing it দেখে তিনিও সেই আচরণে যুক্ত হয়ে পড়েন।
৪. Acute Stress Reaction (তীব্র মানসিক চাপের প্রতিক্রিয়া)
সংজ্ঞা: হঠাৎ মানসিক বা শারীরিক চাপের ফলে শরীরে কর্টিসল নামক হরমোন অতিরিক্তভাবে নিঃসৃত হয়, যা লড়াই অথবা পালানোর প্রতিক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে।
ফলাফল: এই অবস্থায় ব্যক্তি যুক্তিবিহীন আচরণ করতে পারে, যেমন হঠাৎ চিৎকার, ঝগড়া, ভাঙচুর অথবা সহিংসতা।
বৈশিষ্ট্য: এটি অনেকটা শরীরের “প্যানিক মোড”-এর মতো, যেখানে ভাবনা নয়, কেবল প্রতিক্রিয়া চলে।
এই আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের দেখায়, সহিংসতা অনেক সময় কেবল ‘খারাপ আচরণ’ নয়, বরং একটি মানসিক, স্নায়বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক চাপের জটিল প্রতিক্রিয়া।
তাই সমাধানও হতে হবে শুধুমাত্র শাস্তিনির্ভর নয়, বরং সচেতনতা, চিকিৎসা, এবং সামাজিক সহানুভূতির ভিত্তিতে গড়ে তোলা। সহিংসতার মূল বোঝার চেষ্টা না করে কেবল ফলাফল দমন করলে সমাজে তুষের আগুনই থেকে যাবে, যা যে কোনো মুহূর্তে দাবানলে রূপ নিতে পারে।

সমাধান কি?
বাংলাদেশে অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতার যে ছড়িয়ে পড়া, তা কেবল আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা নয়, বরং সমাজের গভীরে গেঁথে থাকা কাঠামোগত সমস্যার প্রতিচ্ছবি। এই সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজন একটি সমন্বিত, স্তরভিত্তিক কৌশল, যেখানে ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, প্রতিটি সত্তা নিজের ভূমিকা পালন করবে। সমাধান হতে হবে বাস্তবমুখী, দীর্ঘমেয়াদী এবং মানুষের আচরণগত ও মানসিক গঠনের উপর কেন্দ্রীভূত।
প্রথমেই শুরু করতে হবে ব্যক্তির মনোজগৎ থেকে। মানুষ যদি নিজের আবেগ, রাগ ও হতাশা নিয়ন্ত্রণ করতে না শেখে, তাহলে সমাজে সহিংসতা রোধ করা কঠিন হবে। একজন ব্যক্তি যখন প্রতিদিন নানা চাপ ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে যায়, তখন তার মস্তিষ্কে জমে থাকা অস্থিরতা একসময় বিস্ফোরণে পরিণত হয়। তাই কমিউনিটি সেন্টার বা ইউনিয়ন পর্যায়ে কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি (CBT) ও মাইন্ডফুলনেস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা জরুরি। পাশাপাশি, হেল্পলাইন ও মোবাইল অ্যাপভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করলে মানুষ নিজে থেকেই তার সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে।
এরপর আসতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার কথায়। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের ভেতরের মানুষটিকে তৈরি করা। কিন্তু আজকের পাঠ্যক্রম শিশুদের কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে শেখাচ্ছে, সামাজিক সহমর্মিতা ও সহনশীলতা শেখাচ্ছে না। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক ও সংবেদনশীল
শিক্ষা (SEL) কারিকুলামের অন্তর্ভুক্তি। প্রাথমিক স্তর থেকেই যদি ছাত্রছাত্রীদের আবেগ বোঝা, মতভেদ মেনে নেওয়া, এবং দলগত কাজ শেখানো হয়, তাহলে তারা বড় হয়ে সহনশীল নাগরিকে পরিণত হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণেও এই মূল্যবোধগুলো যুক্ত করা দরকার, যেন তাঁরা কেবল শিক্ষক নন, সহমর্মিতা শেখানোর রোল মডেল হয়ে উঠতে পারেন।
অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে সহিংসতা প্রতিরোধের পরিকল্পনা অপূর্ণই থেকে যায়। যে সমাজে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতিদিন বেকারত্ব, আয় বৈষম্য ও গৃহহীনতার মধ্যে দিন কাটায়, সেখানে সহিংসতা কেবল প্রতিক্রিয়া নয়, প্রতিশোধও হয়ে ওঠে। ন্যূনতম মজুরি কার্যকর, ক্ষুদ্র ঋণ সহজলভ্য, এবং সামাজিক আবাসন প্রকল্প সম্প্রসারিত হলে মানুষ অন্তত টিকে থাকার নিরাপত্তা পাবে। তখন সে নিজের মর্যাদা হারানোর ভয় থেকে মুক্ত হয়ে আগ্রাসী আচরণে না গিয়েও নিজের অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ পাবে।
কিন্তু সবকিছু তছনছ হয়ে যায়, যদি আইনের শাসন দুর্বল থাকে। বিচারহীনতা এমন এক অবস্থা, যেখানে অপরাধ উৎসাহিত হয়। বর্তমানে বহু সহিংসতার মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে, বিচার হয় না, কিংবা প্রভাবশালী অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। তাই অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের সংখ্যা বাড়ানো জরুরি। পাবলিক স্পেসে সিসি ক্যামেরা বাধ্যতামূলক করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কার্যকরতা বাড়াতে হবে। একইসঙ্গে পুলিশ ও প্রসিকিউশনের জবাবদিহিতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যেন বিচার কেবল একটি কাগজে আটকে না থাকে।
সমাজের ভেতরে শান্তি রক্ষার একটি বড় মাধ্যম হলো পারস্পরিক সম্পর্ক। আগে পাড়ার বড় ভাই বা স্থানীয় মাতব্বররা ঝগড়াঝাঁটি থামাতেন। এখন এই ভূমিকা হারিয়ে গেছে। তাই নতুনভাবে পাড়া কমিটি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে শান্তি কমিটি গঠন করতে হবে, যারা আগাম মধ্যস্থতার মাধ্যমে ছোট ছোট দ্বন্দ্ব থামাতে পারবে। তারা কেবল বিরোধ মেটাবে না, বরং আলোচনার পরিবেশও তৈরি করবে, যা সমাজে বোঝাপড়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলবে।
সবশেষে, রাজনীতি। সহিংসতার সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ দেখা যায় এখানেই। রাজনৈতিক নেতারা যদি সহিংস ভাষা, ঘৃণা ও বিভাজনের বার্তা দেন, তাহলে সমাজের অন্য স্তরগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। রাজনীতি যদি সহনশীলতার চর্চায় নেতৃত্ব না দেয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে সহিংসতা বৈধতা পেয়ে যায়। তাই সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি “অহিংস আচরণবিধি” স্বাক্ষরিত হওয়া দরকার, যেখানে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেবেন, ঘৃণামূলক ভাষা, উসকানি বা সহিংস কর্মসূচি তাঁরা গ্রহণ করবেন না। ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোকেও এই নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারক হতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব সহিংসতার নয়, বরং সম্প্রীতির প্রতিচ্ছবি হয়।
এই প্রতিটি স্তর আলাদা হলেও, তারা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কোনো একটিকে বাদ দিলে গোটা কাঠামো ভেঙে পড়বে। তাই প্রয়োজন সরকার, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াস। একমাত্র তখনই আমরা এক সহনশীল, মানবিক এবং স্থিতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারব, যেখানে মতভেদ থাকবে, কিন্তু হিংসা নয়; রাগ থাকবে, কিন্তু তার বিকল্পও থাকবে। সহিষ্ণুতা তখন দুর্বলতার নয়, বরং উন্নত মানসিকতার প্রতীক হয়ে উঠবে।
সুস্থ সমাজ গঠনের পথে ফিরে যাওয়াই একমাত্র সমাধান!! সহিষ্ণুতা কেবল একটি নৈতিক গুণ নয়, এটি একটি সামাজিক সুরক্ষা বর্ম, যা মানুষকে মানুষ রাখে। সহিষ্ণুতা মানে কেবল “রাগ নিয়ন্ত্রণ” নয়, বরং অন্যের অবস্থান বোঝা, বিরুদ্ধ মতকে সম্মান করা, এবং ভিন্নতা সত্ত্বেও পাশে দাঁড়ানো। যেখানে এই গুণ অনুপস্থিত, সেখানে সমাজ ভেঙে পড়ে সংঘাতের বৃত্তে; প্রতিদিন ছোট ছোট উত্তেজনা জমতে জমতে একসময় বিষ্ফোরণ ঘটায়।
একটি সহিষ্ণু সমাজ মানে এমন একটি জায়গা, যেখানে রিকশাওয়ালার হাত ধরতে দোকানদার এগিয়ে আসে। যেখানে চায়ের দোকানে গ্লাস কম পড়লেও কেউ আর কারো দিকে চিৎকার করে না, বরং বলে, “কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, কোনো সমস্যা না।” যেখানে ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ চট করে হর্ণ না বাজিয়ে পাশের বৃদ্ধকে রাস্তা পার করে দেন। আর লাইনে আগে যাওয়ার বদলে পেছনের জনকে জিজ্ঞেস করেন, “আপনি আগে আসছেন না?”
এই সমাজ একদিনে গড়া যাবে না। এখানে প্রশাসনের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রতিটি নাগরিকের মধ্যকার নিজস্ব আত্মনিয়ন্ত্রণ, সচেতনতা এবং সহানুভূতির বিপ্লবও জরুরি। এই বিপ্লব হবে নিঃশব্দ, কাগজে থাকবে না, কিন্তু রিকশাওয়ালার মুখের হাসি, ছোট ছেলের কাঁধে হাত, কিংবা এক অপরিচিতের আন্তরিকতা দিয়ে তার প্রমাণ মিলবে।
আমরা যদি চাই একটি মানবিক রাষ্ট্র, তাহলে কেবল আইন দিয়েই তা তৈরি হবে না। গড়ে তুলতে হবে এমন একটি সংস্কৃতি, যেখানে সহিষ্ণুতা দুর্বলতা নয়, বরং সভ্যতার শীর্ষগুণ হয়ে ওঠে।
“সহিংসতা অগ্নিদগ্ধের মতো, একজনের জ্বালা অন্যজনের পোড়ায়। আর সহিষ্ণুতা সেই বৃষ্টি, যা সব জ্বালা নেভায়।” এই বৃষ্টির প্রতীক্ষায় আমরা যেন কেবল চেয়ে না থাকি, বরং নিজেই হই তার প্রথম ফোঁটা।
In a society consumed by rage, tolerance isn’t weakness, it’s our last defense!
রেফারেন্স
1. World Bank. (2023). Bangladesh Poverty Assessment Report 2023.
https://www.worldbank.org/…/bangladesh-poverty-assessment
2. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2024). Labour Force Survey 2024.
http://bbs.portal.gov.bd
3. Transparency International Bangladesh (TIB). (2023). Political Violence and Justice Report.
https://www.ti-bangladesh.org
4. BUET Urban Stress Study. (2023). Impact of Urban Congestion and Stress in Dhaka City.
5. APA. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5).
American Psychiatric Association.
6. Education Watch. (2023). Annual Education Report on Conflict Resolution & Moral Development.
Campaign for Popular Education (CAMPE), Bangladesh.
7. World Values Survey. (2022). Wave 7: Trust & Social Capital in Bangladesh.
https://www.worldvaluessurvey.org
8. UNFPA. (2023). Urbanization and Human Aggression: A Crowding Perspective.
https://bangladesh.unfpa.org
9. University of Dhaka – Dept. of Psychology. (2024). Urban Mental Health and Chronic Stress Survey Report.
10. University of Dhaka – Dept. of Media and Communication. (2023). Youth Exposure to Online Hate Speech and Aggression Tolerance.
11. Dollard, J., et al. (1939). Frustration and Aggression. Yale University Press.
12. Moscovici, S., & Zavalloni, M. (1969). The Group as a Polarizer of Attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 12(2), 125–135.