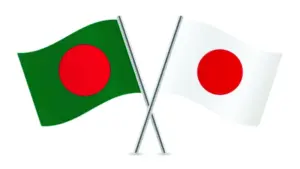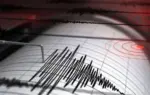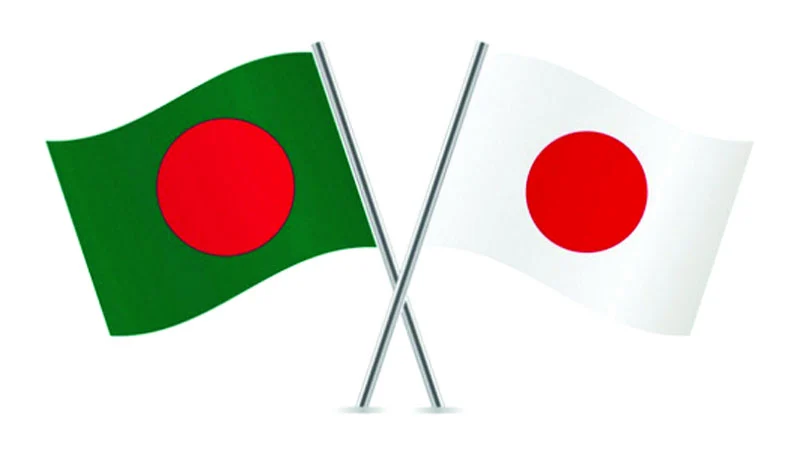লন্ডনে দেড় লক্ষ মানুষের জনসমাগম, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর উত্থান আমাদের কি বার্তা দেয়? বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে এক অদ্ভুত অথচ পরিচিত মধ্যযুগীয় ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে, তার নাম ডানপন্থী জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি উত্থান। প্রথম দর্শনে এই ঢেউ হয়তো কারও কাছে মনে হতে পারে জনগণের প্রকৃত অভিব্যক্তি, মানুষের দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভের বিস্ফোরণ। কিন্তু গভীরে গেলে বোঝা যায়, এ আসলে এক ভয়াবহ বিপদসংকেত, যার শেষ পরিণতি মানবতার পক্ষে শুভ হবে না। কোনো বিশেষ অঞ্চলের কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী হয়তো ক্ষণিকের জন্য এতে আনন্দ পেতে পারে, হিন্দু, মুসলিম কিংবা খ্রিস্টান, কিন্তু পৃথিবী নামে এই নীল গ্রহ তখন ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। ইতিহাস সাক্ষী, যেখানেই ধর্মকে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানেই বিভাজন, সহিংসতা আর নিপীড়ন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।
যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি যেন সেই একই পুরোনো কাহিনির নতুন সংস্করণ। ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে দেশটিতে একাধিক গণবিক্ষোভ ও সহিংস সংঘর্ষ ঘটে গেছে, যার কেন্দ্রবিন্দু অভিবাসন ইস্যু। গতকাল লন্ডনে আয়োজিত Unite the Kingdom নামের বিশাল মিছিলে আনুমানিক এক লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশ নেয়। বাইরের চোখে এটি ছিল কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতিবাদ, কিন্তু ভেতরে ছিল গভীর আতঙ্ক, ভয়, আর ঘৃণার বিষ। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে বহুজন আহত হয়, অন্তত চারজন পুলিশ গুরুতর আহত হন। এই ঘটনাকে ব্রিটিশ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ডানপন্থী সমাবেশ বলা হচ্ছে, আর তার নেতৃত্বে ছিলেন বিতর্কিত টমি রবিনসন। মিছিলকারীরা ব্রিটিশ পতাকার পাশাপাশি “Send them home” প্ল্যাকার্ড বহন করছিলেন, আবার কেউ কেউ আমেরিকার ট্রাম্পপন্থী ক্যাপ মাথায় দিয়েছিলেন। স্পষ্টতই এটি ছিল কেবল স্থানীয় ক্ষোভ নয়, বরং এক আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিধ্বনি।.

বিশ্বজুড়ে আমরা এই প্রতিধ্বনি শুনছি। ভারতের ক্ষেত্রে এর শুরুটা আরও আগেই। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা ছিল এক দাগ কাটার মতো ঘটনা, যা দেখিয়ে দিল রাজনীতির জন্য ধর্ম কতটা কার্যকর অস্ত্র হতে পারে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি যখন ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এলো, তখন থেকে হিন্দুত্বকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় নীতির রূপায়ণ শুরু হলো। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, NRC, রাম মন্দির, সবই ধর্মীয় পরিচয়কে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির কেন্দ্রে বসিয়ে দিল। কোটি কোটি মানুষকে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনে ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়া হলো। কেউ খুশি হলো, কেউ বঞ্চিত হলো, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজটা হলো অস্থির ও ভঙ্গুর।
অন্যদিকে আটলান্টিকের ওপারে, যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থানও সেই একই স্রোতের আরেক সংস্করণ। তার “Muslim Ban”, অভিবাসনবিরোধী নীতি, এবং “America First” স্লোগান আমেরিকার মাটিতে নতুন করে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদকে বৈধতা দিল। ২০২১ সালে ক্যাপিটল হিলে হামলা ছিল এই রাজনীতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ, যেখানে খ্রিস্টীয় জাতীয়তাবাদী আর শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থীরা খোলাখুলিভাবে হামলা চালাল রাষ্ট্রের হৃদয়ে। এ এক ভয়াবহ চিত্র, যা মনে করিয়ে দেয় ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ যখন হাত মেলায়, তখন গণতন্ত্র কতটা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।
ইউরোপও এর বাইরে নয়। ২০১৫ সালের চার্লি হেবদো হামলার পর ফ্রান্সে ইসলামবিরোধী মনোভাব চরমে ওঠে, আর Marine Le Pen-এর জাতীয়তাবাদী দল National Rally অভিবাসনবিরোধী নীতি তুলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইতালিতে জর্জিয়া মেলোনি, পোল্যান্ডে Law and Justice, হাঙ্গেরিতে ভিক্টর অরবান, সবাই একে একে ধর্মকে রাজনৈতিক মূলধন বানিয়ে ফেললেন। শ্লোগান একই: খ্রিস্টীয় ইউরোপকে বাঁচাও।
তবে কেবল খ্রিস্টীয় ডানপন্থার উত্থান নয়, মুসলিম বিশ্বেও আমরা একই প্রবণতা দেখছি, শুধু ভিন্ন রঙে। তুরস্কে এরদোয়ানের ‘একে পার্টি’ ইসলামি মূল্যবোধকে আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে মিশিয়ে “নতুন তুরস্ক” তৈরি করলো। মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড নির্বাচনে জয়ী হলেও সেনা অভ্যুত্থানে টিকতে পারলো না। ইরানে ১৯৭৯ থেকে শিয়া ইসলামিজম রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলভিত্তি হয়ে আছে। পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সবখানেই ইসলামপন্থী দলগুলো জনমত গঠনে সক্রিয়। অনেক সময় এই উত্থান ছিল পশ্চিমা আধিপত্যবিরোধী প্রতিক্রিয়া, আবার কখনো মধ্যপ্রাচ্যের অভ্যন্তরীণ সংকটের ফল।
এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই দুই স্রোত, খ্রিস্টীয় ডানপন্থা আর ইসলামপন্থা, কখনো একে অপরের প্রতিক্রিয়া, আবার কখনো সমান্তরালভাবে চলে। ইউরোপে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভ যত বাড়ছে, মধ্যপ্রাচ্যে ততই ধর্মীয় রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। অর্থাৎ একপক্ষের উগ্রতা আরেক পক্ষের উগ্রতাকে খাওয়াচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে এক দুষ্টচক্র, যার শেষ নেই।
যুক্তরাজ্যের ঘটনায় ফিরে আসি, ২০২৪ সালের Southport ঘটনার কথা মনে করি। তিন কিশোরীর হত্যার ভুল খবর ছড়িয়ে পড়লো যে হত্যাকারী একজন মুসলিম অভিবাসী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইংল্যান্ড জুড়ে অভিবাসনবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো। মসজিদে আগুন, অভিবাসী হোটেলে হামলা, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, সব মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হলো। কিন্তু পরে প্রমাণ হলো তথ্যটা ভুল ছিল। অর্থাৎ ভুয়া খবর, গুজব আর মিথ্যা তথ্যই ছিল সহিংসতার আসল জ্বালানি।
ডিজিটাল যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেন এই উগ্রতার সারথি। Facebook, WhatsApp, Telegram, X (পূর্বে টুইটার), সব জায়গায় ভুয়া খবর আর ঘৃণার প্রচার ছড়িয়ে পড়ছে। টমি রবিনসনের পোস্ট কোটি কোটি ভিউ পাচ্ছে, আবার ইলন মাস্ক নিজেই “UK-তে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য” বলে পোস্ট করছেন। যখন বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মের মালিকরাই ঘৃণার আগুনে ঘি ঢালেন, তখন বোঝা যায় পরিস্থিতি কতটা গুরুতর।
আমাদের দেশের দিকে যদি ফিরে তাকাই তবে, ২০২৪ থেকে ২০২৫ সময়ে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির উত্থান দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে। অর্থনৈতিক চাপ, বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অভিবাসন সংকটকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী “দেশি-বিদেশি শত্রু” ধারণা উসকে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া তথ্য ও ধর্মীয় উস্কানি ছড়িয়ে পড়ায় মসজিদমুখী রাজনীতি এবং জাতীয় পরিচয়ের নামে বিভাজনমূলক বক্তব্য সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছে। রাজনৈতিক দলগুলোও টিকে থাকার জন্য ক্রমশ ধর্মীয় আবহ ব্যবহার করছে, ফলে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা দুর্বল হচ্ছে। এই প্রবণতা বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক পরিসর থেকে সরিয়ে আরও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় মেরুকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
এখন প্রশ্ন হলোঃ এ সবের শেষ কোথায়?
ধর্ম কি রাষ্ট্র পরিচালনার উপযুক্ত ভিত্তি? ইতিহাস বলছে না। ইউরোপের মধ্যযুগের ধর্মীয় যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তানের বিভাজন, সবই প্রমাণ করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিভাজন আর সহিংসতা ছাড়া আর কিছুই দেয় না। তবুও রাজনীতিবিদেরা এই পুরোনো অস্ত্র বারবার ব্যবহার করছেন, কারণ এটি সহজ, সস্তা আর কার্যকর। মানুষের অর্থনৈতিক সংকট, কর্মসংস্থানের সমস্যা বা জলবায়ু বিপর্যয়ের মতো জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তার চেয়ে “অভিবাসীরা আমাদের চাকরি খেয়ে ফেলছে”, “অমুক ধর্ম আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করছে”, এই ধরনের সহজ স্লোগান দিয়ে জনমত অর্জন অনেক সুবিধাজনক।
কিন্তু বাস্তব সমস্যাগুলো কি এতে সমাধান হয়? হয় না। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি, আয়বৈষম্যের প্রসার, প্রযুক্তিগত বেকারত্ব, স্বাস্থ্য সংকট, এসবই রয়ে যায় অনাদৃত। অথচ মানবজাতির টিকে থাকার জন্য এগুলোই আসল চ্যালেঞ্জ। ডানপন্থী ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি মানুষের দৃষ্টি সেখান থেকে সরিয়ে কৃত্রিম শত্রু বানায়, আর মানুষকে বিভক্ত করে।
আজকের পৃথিবীতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক মোড়ে। একদিকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবাধিকার আমাদের নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। অন্যদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ আর ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি সেই সম্ভাবনা নষ্ট করতে উদ্যত। যদি আমরা মানবতার পক্ষে দাঁড়াতে চাই, তবে আমাদের স্পষ্ট করে বলতে হবে, ধর্মের জায়গা ব্যক্তিগত বিশ্বাসে, রাষ্ট্রনীতিতে নয়। রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে হবে যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধ।
ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির অস্থায়ী বিজয় হয়তো কোনো গোষ্ঠীকে আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি মানবজাতিকে এক অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দেবে। পৃথিবী হয়ে উঠবে অবসবাসযোগ্য, কেবল পরিবেশগত দিক থেকে নয়, সামাজিক দিক থেকেও। প্রতিবেশীকে ঘৃণা করা, সহনাগরিককে শত্রু ভাবা, ভিন্নমতকে দমন করা, এসব নিয়ে কোনো সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না।
ইতিহাস আমাদের বারবার সতর্ক করেছে। প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই সতর্কতা শুনবো, নাকি আবারও একই ভুল করবো?
এনামুল হক
১৪-০৯-২০২৫