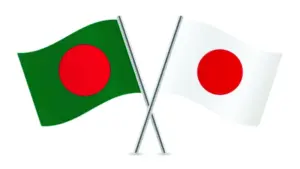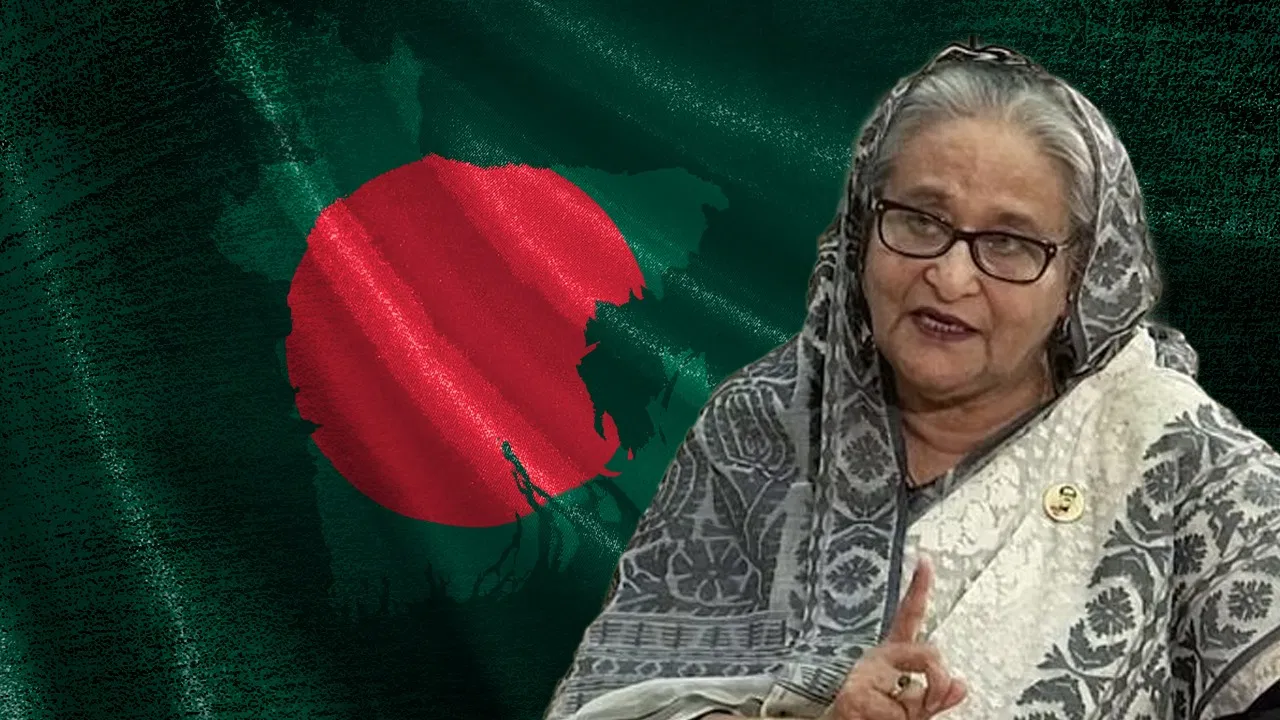বাংলা ভাষায় আমরা প্রায়ই একটি সাধারণ ভুল করি- ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জাতি হিসেবে উল্লেখ করি। “মুসলিম জাতি”, “হিন্দু জাতি”, “খ্রিস্টান জাতি” এমন শব্দবন্ধ আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে এতটাই গা-সওয়া যে কেউ হয়তো কখনো প্রশ্নই তোলেনি এর যথার্থতা নিয়ে। অথচ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ব্যবহার সম্পূর্ণ ভুল। ইসলাম, হিন্দু ধর্ম কিংবা খ্রিস্ট ধর্ম হলো বিশ্বাসের ধারক, জাতি নয়। এই শব্দ ব্যবহারের পেছনে আছে ভাষাগত সরলীকরণ, ইতিহাসের ছায়া, উপনিবেশিক রাজনীতির প্রভাব এবং আরবি থেকে অনূদিত উম্মাহ শব্দের ভুল প্রতিস্থাপন।
‘উম্মাহ’ একটি আরবি শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থ হলো সমাজ বা সম্প্রদায়। ইসলামী ঐতিহ্যে উম্মাহ বলতে বোঝানো হয় বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের একটি আধ্যাত্মিক সমাজ, যারা ভৌগোলিক বা ভাষাগত সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে একই বিশ্বাসে আবদ্ধ। উম্মাহর ধারণাটি মূলত আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক, যা কখনোই জাতিগত পরিচয়ের সমার্থক নয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে “মুসলিম জাতি” হিসেবে, যা ধীরে ধীরে এমন এক ভাষাগত সত্যে পরিণত হয়েছে যে মুসলমানদের বৈচিত্র্যময় জাতিগত, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।
এই বিভ্রান্তি কোনো সাধারণ ভুল নয়; এর গভীরে রয়েছে ইতিহাসের জটিলতা। ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে “Nation” এবং “Community” এই দুটি শব্দের মধ্যে সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট। মুসলমান ও হিন্দুদের রাজনৈতিকভাবে আলাদা পরিচিতি দিতে ব্রিটিশ প্রশাসন কখনো মুসলিমদের ‘Nation’ বলেছে, কখনো ‘Community’। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় “Two-Nation Theory” বা “দুই জাতি তত্ত্ব” এই বিভ্রান্তিকেই রাজনৈতিক হাতিয়ার বানায়। ধর্মকে জাতি হিসেবে দেখার এই ভাষাগত ও রাজনৈতিক অভ্যাসই পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় জায়গা করে নেয়। তাই আজও আমরা স্বাভাবিকভাবে “মুসলিম জাতি” বলি, যদিও মুসলিমরা বাঙালি, আরব, তুর্কি, আফ্রিকানসহ বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বৈশ্বিক ধর্মীয় সম্প্রদায়।
এখানে আরেকটি বড় কারণ হলো ধর্মীয় পরিচয়ের সামাজিক প্রাধান্য। দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষ অনেক সময় নিজেদের জাতিগত পরিচয়ের আগে ধর্মীয় পরিচয়ে চিনতে অভ্যস্ত। “আমি বাঙালি মুসলিম” বলার বদলে “আমি মুসলিম জাতির” মানুষ এই ধারণা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের গভীরে প্রোথিত। দেশভাগের ইতিহাসও এই মানসিকতার পুষ্টি দিয়েছে। পাকিস্তান গঠনের যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছিল ধর্মকে জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে। ফলে এই ভুল ধারণা কেবল ভাষাগত নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার।
ভাষার সরলীকরণের প্রবণতাও এই বিভ্রান্তিকে স্থায়ী করেছে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে বা সাধারণ কথোপকথনে “জাতি” শব্দটি প্রায়ই কেবল “গোষ্ঠী” বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। সমাজবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে। মানুষ সহজ ভাষায় ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও জাতি বলে ডাকে। এর ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে “জাতি” ও “সম্প্রদায়” শব্দ দুটি একে অপরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।
কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে “জাতি” বলতে বোঝানো হয় একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত পরিচয়, যার মূল উপাদান হলো অভিন্ন ভাষা, ভূখণ্ড, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। একটি জাতি গড়ে ওঠে শত শত বছরের সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বাঙালি জাতি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেখানে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে। অপরদিকে “সম্প্রদায়” হলো সামাজিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত একটি গোষ্ঠী, যা বিভিন্ন জাতির মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। মুসলিম সম্প্রদায় বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাই কোনো জাতি নয়; তারা বহু জাতির মানুষের বিশ্বাসের মিলনে গঠিত আধ্যাত্মিক সমাজ। আর “জনগোষ্ঠী” শব্দটি আরও ভিন্ন অর্থ বহন করে, যা সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের সংখ্যা বা বৈচিত্র্যময় জনসমষ্টিকে বোঝায়।
বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে এই ভুল ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে আরবি শব্দ “উম্মাহ”-র সরল অনুবাদের কারণে। ইসলামে উম্মাহর ধারণা ছিল বিশ্ব মুসলিমদের আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক, কিন্তু বাংলা অনুবাদে যখন এটাকে “জাতি” বলা হলো, তখন ধর্মীয় পরিচয় জাতিগত পরিচয়ের সমান মর্যাদা পেয়ে গেল। মানুষ “বাঙালি মুসলিম” হওয়ার চেয়ে “মুসলিম জাতি” বলেই নিজেদের সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করল। এর ফলে ধর্মীয় ঐক্যের ভাবনা জাতিগত বৈচিত্র্যকে ছাপিয়ে গেল।
এই ভাষাগত প্রবণতা আমাদের সমাজবোধের গভীরে প্রভাব ফেলেছে। পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে ধর্মীয় পরিচয়ের অতিরিক্ত গুরুত্বের কারণে বহু সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়েছে। অথচ জাতি, সম্প্রদায় এবং জনগোষ্ঠীর সঠিক পার্থক্য বোঝা গেলে আমরা দেখতে পাই- ধর্মীয় পরিচয় কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত এক সম্প্রদায়, যা বহু জাতির মানুষের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।
ভাষা হলো চিন্তার আয়না। আমরা যেভাবে শব্দ ব্যবহার করি, তা আমাদের মানসিক কাঠামোকেও গড়ে তোলে। উম্মাহকে যদি “ধর্মীয় সম্প্রদায়” বা “সমাজ” বলা হতো, তবে হয়তো আমরা ধর্মীয় ঐক্যের ধারণা বজায় রেখেও জাতিগত পরিচয়ের বৈচিত্র্য অস্বীকার করতাম না। শব্দচয়ন কখনও শুধু ভাষার বিষয় নয়; এটি আমাদের রাজনীতি, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের প্রতিচ্ছবি। তাই “মুসলিম জাতি” বলার এই ছোট্ট ভাষাগত ভুল আসলে দক্ষিণ এশিয়ার শত বছরের বিভাজন, রাজনীতির চাতুর্য আর সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তির বহিঃপ্রকাশ। আমাদের এই বিভ্রান্তি দূর করার শুরু হতে পারে ভাষা থেকে, কারণ সঠিক শব্দচয়ন শুধু ব্যাকরণের শুদ্ধতা নয়, আত্মপরিচয়ের স্বচ্ছতাও ফিরিয়ে আনে।
সবচেয়ে সঠিক এবং উপযুক্ত শব্দ হলো “মুসলিম সম্প্রদায়”। এটি মুসলিমদের একটি বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব ও সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রকাশ করে, যা তাদের প্রধান পরিচয়। যখন নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বলতে চাই, তখন “বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠী” বা এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।