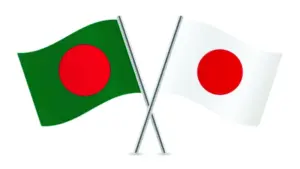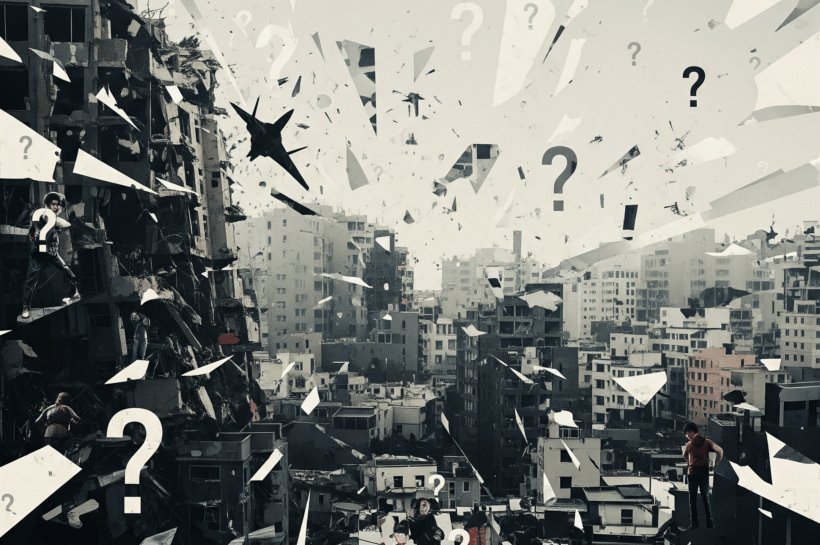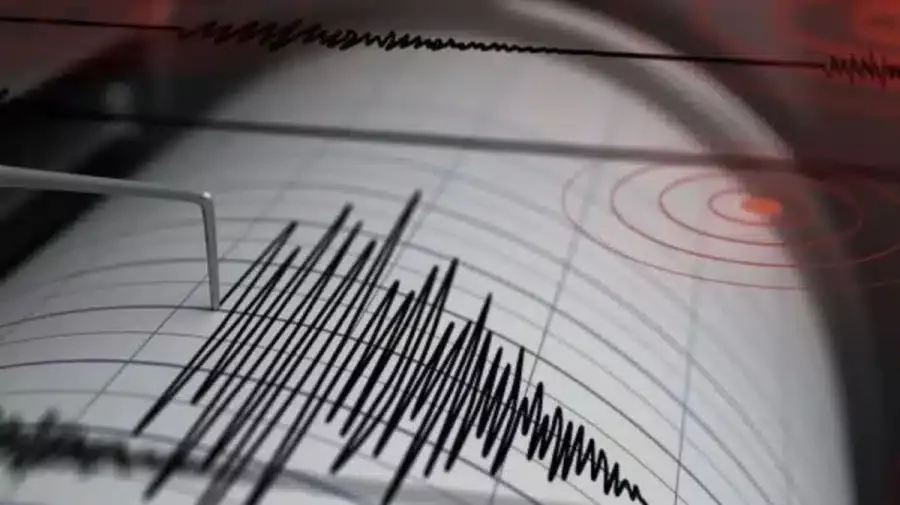গত দুদিন ধরে অনলাইনে প্রচুর এনালাইসিস দেখছি যেগুলি কোনটাই বাস্তবিক জ্ঞানপ্রসুত মনে হচ্ছেনা। একারণেই পাইলট হিসেবে এই পোস্টটি লেখার প্রয়োজন বোধ করলাম। প্রথমেই কিছু মিথ ভাঙ্গা যাক।
১) পাইলট মাইলস্টোনের মাঠে অবতরণ করতে চেয়েছিল। এটা রিতিমত হাস্যকর, কেননা এরকম একটা যুদ্ধবিমান অবতরণের জন্যে এমনকি ১ কিমি লম্বা মাঠও যথেষ্ট না। তাছাড়া মাইলস্টোনের মাত্র ১ কিমি পশ্চিমেই তুরাগ নদির ওপারে প্রচুর খোলা জায়গা ছিল।
২) ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ট্রেনিং কেন? আসলে ট্রেনিং ম্যানুভারগুলি সাধারণত হয় শহরের বাইরে, কিন্তু উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য তো কোনো না কোনো রানওয়েতে ফিরতেই হয়।
৩) বিমানটি ছিল অতি পুরোনো, জং ধরা। ধরে নিচ্ছি বিমানটির ফিটনেস ছিল। ফিটনেস থাকলে যেকোনো বিমানের ক্ষেত্রেই বয়স কোনো ব্যাপারই না। একটা বিষয় অনেকেই হয়তো জানেন না, বিমান কোনো গাড়ি বা মুড়ির টিন বাস নয়। বিমানের প্রতিটা যন্ত্রাংশের একটা বয়সসীমা থাকে। যন্ত্রাংশভেদে সেই বয়সসীমা ৫০ থেকে শুরু করে ৩০০০ ঘণ্টা হতে পারে। বিমানটি কত ঘণ্টা ওড়ানো হলো সেটি হিসাব করে যন্ত্রাংশগুলো নিয়মিত পাল্টাতে হয়, নতুবা বিমানের ফিটনেস (Airworthiness) বাতিল হয়ে যায়। এছাড়াও প্রতিটা বিমান প্রতি ৫০ থেকে ১০০ ঘণ্টা ওড়াবার পর প্রতিটা যন্ত্র পরীক্ষা করে সার্টিফাই করাতে হয়। একারণেই সেকেন্ড হ্যান্ড বিমানের বাজার ঘাঁটলে দেখবেন, যতক্ষণ একটা প্লেনের ফিটনেস আছে, একই মডেলের ১৯৬০ সালে নির্মিত বিমান এবং ২০০০ সালে নির্মিত বিমানের মধ্যে দামের খুব একটা ফারাক পাবেন না। খোদ আমেরিকান এয়ারফোর্সেও অনেক জায়গায় এখনো T-35 Talon বিমানটি ব্যবহৃত হয়, যেগুলি তৈরি হয়েছিল ১৯৬১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত।
৪) বিমানবন্দরের এতো কাছে‚ বিশেষ করে রানওয়ে বরাবর এতো উচু বিল্ডিং কেন? এটা যৌক্তিক প্রশ্ন এবং এটির সাথে নগর পরিকল্পনা জড়িত। কিন্তু ভুলে যাবেন না বিমানটি কিন্তু কোন উচু বিল্ডিং আঘাত করেনি বরং বিধ্বস্ত হয়েছে একটি দোতলা বিল্ডিং এর উপর। তাই উচু ইমারতগুলি এই দূর্ঘটনার জন্য সরাসরিভাবে দায়ী নয়।
আসুন এই দুর্ঘটনার ফ্যাক্টগুলির বিশ্লেষণ করি। ISPR থেকে আমরা জানছি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির তেজগাঁও বিমান ঘাটি থেকে প্লেনটি নিয়ে আকাশে উঠেন দুপুর ১ টা ৬ মিনিটে। এটি তার প্রথম সলো ফ্লাইট ছিল অর্থাৎ কোন প্রশিক্ষক ছাড়া বিমান চালনা তার এটাই প্রথম। আমরা আরো জানতে পারি উড্ডয়নের কিছুক্ষন পরেই সে রেডিওতে যান্ত্রিক ত্রুটির কথা জানায় এবং ঘাটিতে ফেরার চেষ্টা করতে গিয়ে বিমানটি ভূপাতিত হয়।
একজন নতুন পাইলটকে সলো ফ্লাইট বা একা বিমান চালনার অনুমতি দেয়া হয় তখনই যখন সে মোটামুটিভাবে একটা বিমান উড্ডয়ন করতে পারে‚ পথ খুজে নেয়া বা ন্যাভিগেশনের নুন্যতম পারদর্শীতা দেখাতে পারে এবং সে বিমানটি নির্বিঘ্নে অবতরণ করাতে পারে। ধরে নেয়া যায় প্রশিক্ষকের সাথে এর আগেও বহুবার এই তিনটি যোগ্যতা প্রমাণের পরেই সে তার সলো ফ্লাইটের অনুমতি পেয়েছিল। আসলে এই স্তরে থাকা কোন পাইলটেরর কিন্তু এমনিতেই ইমারজেন্সি বা কোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো পারদর্শিতা থাকে না। সেই অনুশীলনগুলি আসে আরো পরে।
সবার বোঝার সুবিধার্থে কিছু বিষয় জানিয়ে রাখি। পাইলটদের একেবারেই শুরু থেকেই উড্ডয়নের তিনটি মূলনীতি শেখানো হয়। প্রাধান্যের ক্রমানুসারে সেগুলি হলো Aviate‚ Navigate and then Communicate অর্থাৎ প্রথমেই মনোযোগ দাও উড্ডয়নের দিকে এরপর ঠিক করো কোন দিকে যাবে এবং সবশেষে টাওয়ারের সাথে বা ইমার্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করে নিজের পরিস্থিতি ও প্ল্যান জানাও। কোন বিমান কিন্তু হঠাৎ টুপ করে আকাশ থেকে পড়ে যায় না। এমনকি ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেলেও না। বৈমানিকদের প্রশিক্ষনের একটা অংশই কিন্তু থাকে ইঞ্জিন অকেজো হয়ে গেলে বা ইঞ্জিনে আগুন লাগলে কি করতে হবে সেই প্রশিক্ষণ‚ যদিও সেগুলি সবই আসে সলো ফ্লাইটের আরো পরে। বিমান যদি কোন ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে অথবা প্রচন্ড ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে টুকরো টুকরো হয়ে না যায় তাহলে ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেলেও সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং গ্লাইডিং দুরত্বের মধ্যে কোন রানওয়ে থাকলে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে অবতরণ করাও সম্ভব।
ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেলে পাইলটকে মূলত তিনটি কাজ করতে হয়:
১) Aviate: বিমানের বেগ পরিবর্তন করে এমন একটি গতিতে আনতে হয় যে গতিতে প্লেনটি সবচেয়ে দীর্ঘক্ষণ গ্লাইড করে আকাশে ভাসবে। প্রতিটি বিমানের ক্ষেত্রে এই বেগ ভিন্ন। এটিকে বিমানটির Best glide speed বলে।
২) Navigate: এর পরই বিমানের বর্তমান উচ্চতা মাথায় রেখে পাইলটকে হিসেব করতে হয় এই গতিতে সে সর্বোচ্চ কতদূর উড়তে পারবে এবং সেই সীমার মধ্যে যদি কোন বিমানবন্দর থাকে তাহলে তো খুবই ভাল কথা আর তা না থাকলে তাকে খোলামেলা কোন মাঠের সন্ধান করতে হয় বা এমন কোন জায়গা যেখানে মানুষ হতাহতের সম্ভাবনা থাকবে সর্বনিম্ন।
৩) Communicate: সবশেষে পাইলট যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে সে কি করতে চাইছে তখন সে তার সিদ্ধান্ত ও পরিস্থিতি জানাবে কনট্রোল টাওয়ারকে যেন তারা জরুরি ব্যবস্থা নিতে পারে বা সাহায্য পাঠাতে পারে।
বিমান যখন ভূপাতিত হয় তখন সেই দুর্ঘটনাকে বৈমানিকরা সাধারণত দুটো ভাগে ফেলে। ইঞ্জিন কাজ না করলেও অক্ষত বিমান যখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভূপাতিত হয় তখন এর সবচেয়ে বড় কারণ থাকে স্টল-স্পিন দুর্ঘটনা। এটি মূলত পাইলটের ভুলের কারণে হয় যেগুলির মধ্যে ন্যূনতম গতিবেগ ধরে রাখার অপারগতা, খুব তীক্ষ্ণভাবে অথবা রাডারের সাথে সামঞ্জস্যহীনভাবে টার্ন নেওয়া অন্যতম। এভাবে নিয়ন্ত্রণ হারালেও সেই নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া সম্ভব যদি প্লেনের যথেষ্ট উচ্চতা থাকে, অর্থাৎ হাতে যথেষ্ট সময় থাকে। বিমানটি যদি মাটির খুব কাছে থাকে তাহলে স্টল বা স্পিন থেকে আর রক্ষা নেই। বিমান ভূপাতিত হওয়ার সময় পাইলটরা সব সময় চেষ্টা করে যেন মাটি স্পর্শ করে বিমান সম্পূর্ণ স্থির হওয়ার আগ পর্যন্তও যেন বিমানের নিয়ন্ত্রণ পাইলটের হাতে থাকে। এটাকে পাইলটদের ভাষায় কন্ট্রোল্ড ফ্লাইট ইনটু টেরেইন (Controlled flight into terrain) বলে। সম্প্রতি আমরা ভারতে এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনায় এমনটি হতে দেখেছি। মাটিতে আঘাত পাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বিমানটিকে কোনো রকম ডিগবাজি খেতে দেখা যায়নি, নিয়ন্ত্রণ ছিল পাইলটদের হাতে যদিও ইঞ্জিন অকেজো থাকায় তাদের আর কিছুই করার ছিল না এবং বিমানটি গ্লাইড করে এসে ভূপাতিত হয়।
এবার তাহলে এই আলোকে মাইলস্টোন দূর্ঘটনার বিশ্লেষণ করা যাক। ISPR এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী পাইলট টের পেয়েছিল যে বিমানটি ঠিক মতো কাজ করছে না এবং সে বেইজে ফিরতে চাইছিল। যদিও আমি মনে করি সে তেজগাঁও বেইজে না বরং শাহ জালাল এয়ারপোর্টে অবতরণের চেষ্টা করছিল কেননা সেই রানওয়েই ছিল তার সব চাইতে কাছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে যখন সে টের পেল যে তার বর্তমান উচ্চতা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গ্লাইড করে পৌছানো সম্ভব না এবং তার আগেই প্লেন ভূপাতিত হবে তখন সে কি করলো? পাইলট হিসেবে তখন তার কর্তব্য ছিল এয়ারপোর্টে পৌছানোর সেই চেষ্টা বাদ দিয়ে মাইলস্টোনের মাত্র এক কিলোমিটার পশ্চিমে তুরাগ নদীর ওপারে খোলা মাঠে অবতরণের চেষ্টা করা অথবা সেদিকে বিমানটি ধাবিত করে ইজেক্ট করা। সেটি করলে এতোগুলি শিশু আজ হতাহত হতো না এবং সে নিজেও হয়তো প্যারাশুটের কারণে বেচে যেত।
ধরে নিচ্ছি সে অতটা নির্বোধ ছিল না এবং সে ভেবেছিল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গ্লাইড করে পৌছানো সম্ভব। তাহলে প্রশ্ন জাগে রানওয়ে থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে তাহলে বিমানটি ভূপাতিত হলো কেন। এর একটাই সম্ভাবনা মনে আসে আর সেটি হলো স্টল-স্পিন দূর্ঘটনা। যেহেতু এটি ছিল একটা ট্রেনিং ফ্লাইট তাই ধরে নিচ্ছি পাইলটের ম্যানুভার করার কথা ছিল দীয়াবাড়ির পশ্চিমের খোলা যায়গায়। সেখান থেকে শাহ জালাল বিমানবন্দরে আসতে হলে প্রথমে তাকে যেতে হবে পূব দিকে এবং রানওয়ে থেকে ৩-৪ কিমি উত্তরে (ঠিক যেখানে মাইলস্টোন স্কুলটি অবস্থিত) থাকা অবস্থায় তাকে ৯০ ডিগ্রি টার্ণ নিয়ে রানওয়ের সাথে লাইনআপ করতে হবে। পাইলটদের ভাষায় এই টার্নকে Base To Final Turn বলে। এই টার্ণের সময় বিমানের গতি থাকে সবচেয়ে কম এবং স্টল স্পীডের খুব কাছাকাছি এবং ঐতিহাসিক ভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সংখ্যক বিমান দূর্ঘটনা হয়েছে এই Base to final টার্ণের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে Stall Spin দূর্ঘটনায় যেখানে বিমান গোত্তা খেতে খেতে নেমে আসে এবং রিকভারি করার মতো সময় পাওয়া যায়না। বিমানটি ঠিক কোন দিক থেকে উড়ে এসে ঠিক কোন বিল্ডিংএ আঘাত করেছে ‚ আঘাতের সময় বিমানটি কি সোজা ছিল নাকি কাত বা উল্টে ছিল সেসব নিরিক্ষা করলে সহজেই Stall Spin হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত করা সম্ভব। হতে পারে পাইলট যখন টার্ন নেয়ার সময় নিয়ন্ত্রন হারায় তখন সে ইজেক্ট করে কিন্তু ইজেক্ট করতে বেশি দেরী করে ফেলায় অথবা ইজেকশনের সময় প্লেন কাত বা উল্টো হয়ে থাকার কারণে ইজেকশন সীট তাকে উপরের দিকে ছূড়ে না মেরে এক পাশে বা নিচের দিকে ছুড়ে মারে যার দরুন তার মৃত্যু হয়।
তাহলে আমরা নিচের সিদ্ধান্তে আসতে পারি যেগুলির একটি বা একাধিক সত্য হবার কারণে এই ট্র্যাজেডি ঘটেছে:
১) পাইলট হিসেব করতে ভুল করেছে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গ্লাইড করে পৌছানোর মতো যথেষ্ট উচ্চতা তার আছে কিনা। সেটি হলে এর দায় পাইলটের অভিজ্ঞতার অভাব।
২) যখন সে অনুধাবন করেছে রানওয়ে পর্যন্ত পৌছুতে পারছে না তখন সে বিমানের নাক সামান্য ঘুরিয়ে মাত্র ১ কিমি পশ্চিমের খোলা মাঠ বেছে নেয়নি। আমি এটি বিশ্বাস করতে চাইনা কেননা এটি সত্য হলে পাইলটকে রিতিমত সাইকো বলতে হবে।
৩) হিসাব মতে বিমানটির যথেষ্ট উচ্চতা ছিল কিন্তু Base to Final টার্নের সময় পাইলট নিয়ন্ত্রন হারায়। সম্প্রতি প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজেও বিমানটিকে গোত্তা খেতে খেতে নিচে পড়তে দেখা যায়‚ যা স্টল স্পিন দূর্ঘটনার দিকেই আঙ্গুল তোলে। এটি সত্য হলে এর একমাত্র কারণ পাইলটের দক্ষতার অভাব ও অনভিজ্ঞতা।
৪) সর্বশেষ সম্ভাবনা হলো পাইলট ইচ্ছে করেই মাইলস্টোনের দিকে বিমান তাক করেছিল অথবা বিকল্প থাকা সত্যেও জেনে বুঝেও মাইলস্টোনের দিক থেকে দিক পরিবর্তন করেনি। পাইলট সুইসাইড বলে একটা কথা আছে যেখানে পাইলট ইচ্ছে করেই মরে এবং মারে। এরকম ঘটনা আগেও হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়ার দূর্ঘটনাও সেদিকেই দিক নির্দেশ করছে। এরকম ঘটনার পিছনে থাকে মূলত পাইলটের মানসিক স্বাস্থ্য।
বিমানটির ট্রান্সপন্ডার থেকে প্রাপ্ত জিপিএস রাডার ডাটা ‚ কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে কথোপকথন‚ তার মিশন প্ল্যান‚ ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডারে (যদি থেকে থাকে) প্রাপ্ত তথ্য‚ এবং ধ্বংসাবশেষের সুষ্ঠ নিরীক্ষা করলে সহজেই এই তদন্ত শেষ করা সম্ভব।
যান্ত্রিক ত্রুটির কথা যেহেতু বলা হচ্ছে‚ অবশ্যই বিমান পরিচর্যায় নিয়োজিতদের দায় এখানে আছে এবং যারা এয়ারপোর্টের রানওয়ে বরাবর এতো উচু উচু ইমারত নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে তাদেরও দায় আছে‚ যদিও বিমানটি কোন উচু ইমারত নয় বরং একটা দোতলা বিল্ডিংএ আঘাত করেছে। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে দুর্ঘটনা হয়তো ঠেকানো যেত না কিন্তু তার পরেও পাইলটের কিছু ভুল না হলে সেই দূর্ঘটনার কারণে এতোগুলো প্রাণ আজ হারাতে হতোনা।