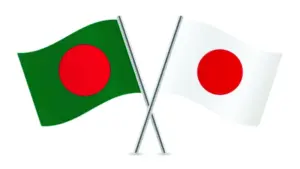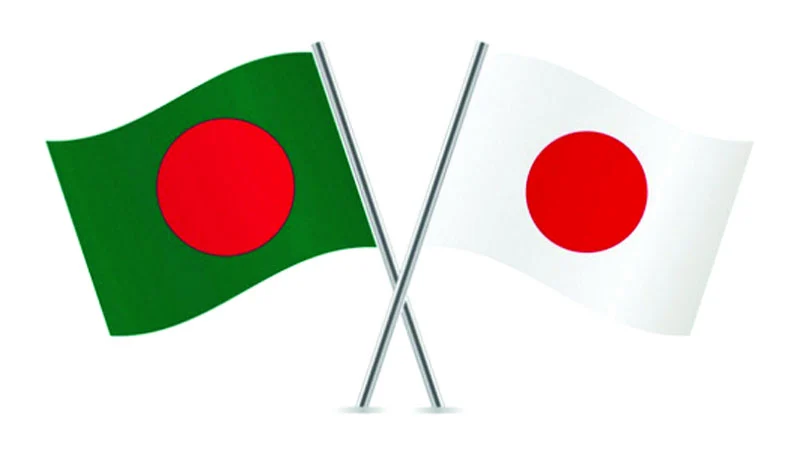পুলিশকে প্রাণঘাতী অস্ত্র কেন দেওয়া হয়? বিবিসির সাম্প্রতিক প্রতিবেদন নিয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুলিশকে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহারের জন্য প্রাণঘাতী অস্ত্র (Lethal Arms) দেওয়া হয়। ব্রিটিশ পুলিশেরও এমন অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি আছে পরিস্থিতি অনুযায়ী। কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশের ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজনেও এর ব্যবহার না হয়, তাহলে তাদের কেন এই অস্ত্র দেওয়া হলো? বিশ্বব্যাপী পুলিশকে কেন প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া হয়? এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, একটি খণ্ডিত অডিও ক্লিপকে কেন ‘এডিট নয়’ বলে দাবি করছে বিবিসি?
যখন বাংলাদেশে ‘মব সন্ত্রাসের’ বিষয়টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে, ধর্ষণ মহামারী আকার ধারণ করেছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে, ঠিক সেই সময়ে পুরনো একটি বিতর্কিত অডিও ক্লিপ নতুন করে ভাইরাল করার পেছনে কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেছে? এই প্রশ্নগুলোই সামনে এসেছে সম্প্রতি বিবিসির একটি প্রতিবেদনের পর।
বিবিসির ‘অনুসন্ধানী প্রতিবেদন’ এবং বিতর্ক
৯ জুলাই ২০২৫, বিবিসি “Ex-Bangladesh Leader authorised deadly crackdown, leaked audio suggests” শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এটিকে তারা ‘বিবিসি আই’ এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হিসেবে দাবি করছে। বিবিসির ভাষ্যমতে, তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ফাঁস হওয়া অডিও কল ‘ইয়ারশট’ নামের অডিও এক্সপার্ট দ্বারা যাচাই করেছে এবং নিশ্চিত হয়েছে যে অডিওটি এডিট বা ম্যানিপুলেট করা হয়নি। এর ওপর ভিত্তি করেই বিবিসি শিরোনাম করেছে যে শেখ হাসিনা ক্র্যাকডাউনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রধান প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় আন্দোলনকারীদের ওপর প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে বিতর্কিত ফোনকলের অডিও ফাঁস হয়েছে, তা কোনো বিদেশি গণমাধ্যম বিবিসি দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়নি, বরং ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি উদ্ধার করা হয়েছে।
স্বাভাবিকভাবেই বিবিসির মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের এমন শিরোনামের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শিবিরে আনন্দের ঢেউ লেগেছে। তারা মনে করছে, এই শিরোনামটিই তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট, কারণ অনেকেই পুরো খবর পড়ার ধৈর্য রাখেন না।
ফরেনসিক বিশ্লেষণ ও অডিওর খণ্ডিতাংশ নিয়ে প্রশ্ন
বিবিসির দাবি অনুযায়ী, ফরেনসিক এক্সপার্ট ইয়ারশট বলেছেন যে এই অডিও এডিটেড বা ম্যানিপুলেটেড নয়। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে: অডিওটি যদি একটি কথোপকথনের খণ্ডিতাংশ হয় (যেমন, মাত্র ১৮ সেকেন্ড), তাহলে পুরো কথোপকথন থেকে শুধুমাত্র এই অংশটুকু লিক করা হলে তা ‘এডিটেড’ হয় না কীভাবে? পুরো কথোপকথন যার কাছে ছিল, তিনি নিশ্চয়ই বাকি অংশ বাদ দিয়েছেন। তাহলে এটি কীভাবে ‘নন-এডিটেড’ বলে দাবি করা হয়? ‘এডিট’ মানে শুধুমাত্র কাটছাঁট নয়, বরং কোনো তথ্যের আংশিক উপস্থাপনাও তথ্যের সম্পূর্ণতাকে বিঘ্নিত করতে পারে।
বিবিসি আরও দাবি করেছে যে অডিওটি ১৮ জুলাইয়ের। এর উৎস হিসেবে তারা “a source with knowledge of leaked audio” এর কথা উল্লেখ করেছে। প্রশ্ন হলো, একটি অডিওর ফরেনসিক বিশ্লেষণ করলে তার উৎপত্তি এবং সময় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার কথা। তাহলে ইয়ারশটের কাছ থেকে অডিওর সত্যতা সম্পর্কে মতামত নিতে পারলেও, এটি কবেকার অডিও, তার জন্য কেন একজন ‘ইন্টারনাল সোর্স’-এর প্রয়োজন হলো? এই বিষয়ে ইয়ারশটের কোনো মন্তব্য কেন নেই?
বিবিসি যদি দাবি করে যে তাদের কাছে ফাঁস হওয়া অডিও সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন ‘ইন্টারনাল সোর্স’ আছে, তাহলে কেন তারা পুরো অডিওটি উদ্ধারের চেষ্টা করলো না? ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য ইয়ারশটের মতো প্রতিষ্ঠানকে তারা ভাড়া করতে পারলো, কিন্তু সোর্স থাকা সত্ত্বেও তারা কেন পুরো অডিওটি পেলো না? পুরো অডিওটি পাওয়া গেলে তবেই একে সত্যিকারের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলা যেত।
১৮ সেকেন্ডের অডিও এবং প্রাসঙ্গিকতার অভাব
প্রকাশিত ১৮ সেকেন্ডের খণ্ডিত অডিওটিতে কার সাথে কথা বলা হয়েছে, কাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কাদের গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে এবং কোন প্রেক্ষাপটে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে—তার কিছুই উল্লেখ নেই। তাহলে বিবিসি কীভাবে ধরে নিল যে এখানে সাধারণ আন্দোলনকারীদের কথা বলা হয়েছে? নিশ্চিতভাবেই এটি একটি বক্তব্যের খণ্ডিতাংশ। যারা এটি প্রকাশ করেছে, তাদের কাছে নিশ্চয়ই পুরো বক্তব্যটি আছে। যদি তাদের উদ্দেশ্য সৎ হয়ে থাকে, তাহলে কেন শুধুমাত্র এই অংশটি প্রকাশ করা হলো? বাকি অংশ প্রকাশ করলে সমস্যা কোথায় ছিল?
প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ও সময়কাল নিয়ে বিতর্ক
বিবিসির এই প্রতিবেদনকে ‘অনুসন্ধানী প্রতিবেদন’ বলা হলেও, এতে নতুন এমন কিছু নেই যা গত ১১ মাসে বারবার বলা হয়নি। জাতিসংঘের যে ফরমায়েশি এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল, এর থেকে এটি আলাদা কিছু নয়। যে অডিও কলের কথা বলা হয়েছে, সেটি মার্চ মাসেও প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তখন তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। তাই বিবিসির মোড়কে “উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিরোনাম” দিয়ে এটিকে নতুন করে সামনে আনা হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এই সময়ে এসে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হলো? এর সময়কাল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইউনুস সরকারের আলোচনার ব্যর্থতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন করে ৩৫% শুল্ক আরোপ করা হয়েছে দু’দিন আগে, যা দেশের নাজুক অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। দেশে ধর্ষণ মহামারী আকার ধারণ করেছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও বাংলাদেশের ‘মব সন্ত্রাসের’ বিষয়টি জোরেশোরে আলোচিত হওয়া শুরু হয়েছে। চারদিক থেকে ইউনুস সরকার যখন চাপে পড়েছে, তখনই বিবিসির এই প্রতিবেদনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সবকিছু আড়ালে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত এগারো মাস ধরেই তাদের এই আইওয়াশ রাজনীতি চলছে বলে দাবি করা হচ্ছে।
অডিওর সত্যতা এবং ডীপ ফেইকের সম্ভাবনা
বর্তমানে ডীপ ফেইকের (Deep Fake) রমরমা অবস্থার মধ্যে ট্রাম্প, পুতিন, মোদী, শি জিনপিং, এলন মাস্ক বা পৃথিবীর এমন কোনো পরাক্রমশালী নেতা বা ব্যক্তিত্ব নেই যাদের নামে ডীপ ফেইক অডিও/ভিডিও দিয়ে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে না। এমতাবস্থায়, এই অডিওটিকে অনেকেই ডীপ ফেইক মনে করছেন। আবার অনেকেই এটিকে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে সংঘঠিত হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার সময়ের অডিও বলে দাবি করে তথ্য প্রমাণ হাজির করছেন।
কিন্তু বিবিসির মতো ঐতিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এসবের তোয়াক্কা না করে অডিওটি বাজারে ছেড়ে ভাইরাল হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি। সব পক্ষের বক্তব্য ছাড়া এমন একটি খন্ডিত ভিডিওকে ‘এডিট নয়’ দাবি করে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন কিভাবে সংবাদ প্রকাশ করে—এই প্রশ্নও এখন সচেতন মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে।