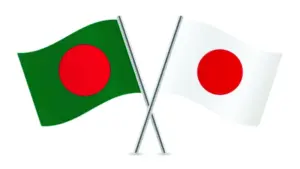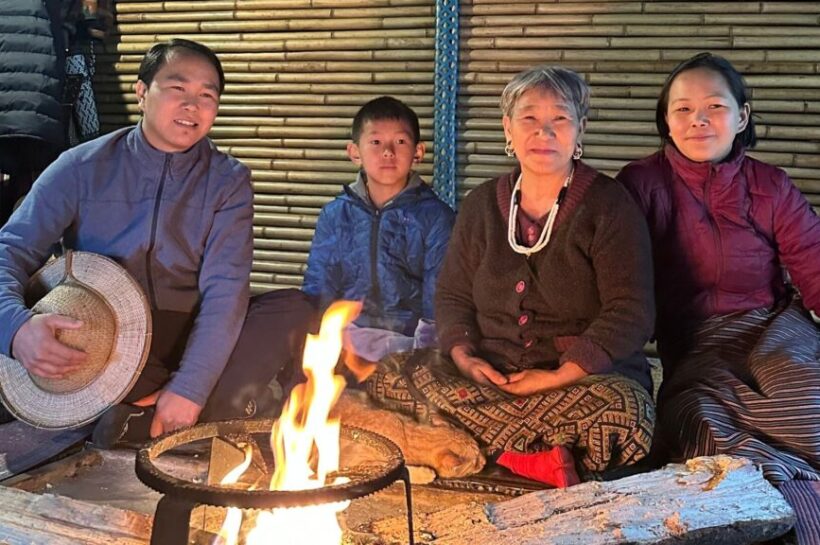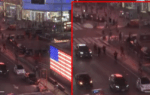আদিবাসীরা এখনও আদি-সাম্যবাদী সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে। যেমন উৎপাদনের উপকরণ (ভূমি, বন, পানি) ব্যক্তিগত মালিকানায় নয়, বরং গোত্র বা কমিউনিটির যৌথ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে শ্রেণীভেদ তৈরি হয়না, কারণ এই ব্যবস্থায় সম্পদের উপর ব্যক্তিগত একচেটিয়া মালিকানার সুযোগ থাকে না।
একইভাবে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক আদিবাসীদের “পরিষদ” ও প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে, যেখানে নেতৃত্বে নারী-পুরুষ সমানভাবে বা যৌথভাবে অংশ নিতে পারে। সাম্যবাদী প্রথা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমতার মূল্যবোধ জাগিয়ে রাখে, যা বংশানুক্রমে যৌথ উৎসব, পারস্পরিক সহায়তা, এবং পারিবারিক কাঠামোয় মাতৃতান্ত্রিক বা সমতাভিত্তিক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।
তবে বাইরের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তির প্রভাবে আদিবাসী সমাজে শ্রেণীভেদ প্রবেশ করেছে। আধুনিক কৃষি ও বাজার অর্থনীতি অনেক দেশে ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ দেয়, যা আদিবাসীদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের বিভাজন তৈরি করছে। রাষ্ট্রের ভূমি-নীতি, বহিরাগতদের জমি দখল, এবং দালাল-মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উত্থান – সব মিলিয়ে ঐতিহ্যগত সামাজিক মালিকানা ব্যবস্থায় ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। ফলে কিছু পরিবার বা ব্যক্তি অধিক সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জন করে, অন্যরা বঞ্চিত হয়, এবং এভাবে আদিবাসী সমাজে শ্রেণী তৈরি হয়।
অন্যদিকে পিতৃতন্ত্রের অনুপ্রবেশ মূলত দুই পথে হচ্ছে:
এক, উপনিবেশবাদী ও রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোর মাধ্যমে, যেখানে পুরুষপ্রধান নেতৃত্ব ও উত্তরাধিকার প্রথা চাপিয়ে দেওয়া হয়। দুই, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে, যা নারীর ভূমিকা সীমিত করে। নারীকে শিক্ষার সুযোগ, বাজারে অংশগ্রহণ ও সমাজে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় থেকে বঞ্চিত করে। বাইরের সমাজর পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতা আদিবাসী সংস্কৃতিতেও ঢুকে পড়ে। ফলে কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীতে আগের সমতাভিত্তিক বা মাতৃতান্ত্রিক ধারা ভেঙে গিয়ে পুরুষতান্ত্রিক শ্রেণীভিত্তিক বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে। যা মূলত পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রের আধিপত্যের কারণে।
আদিবাসী সমাজে শ্রেণী ও পিতৃতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কয়েকটি ধাপে:
প্রথম ধাপ (আদি সাম্যবাদী যুগ): অধিকাংশ আদিবাসী সমাজে জমি, বন, পানি ও শিকারক্ষেত্র ছিল সমষ্টিগত মালিকানায়, যেখানে উৎপাদন ও ভোগের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। পরিবার ও গোত্রের মধ্যে সমতার সম্পর্ক বজায় থাকত, এবং অনেক গোষ্ঠীতে মাতৃতান্ত্রিক বা সমতাভিত্তিক পারিবারিক কাঠামো ছিল, যেখানে নারী-পুরুষ উভয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পদ ব্যবহারে সমান অধিকার ভোগ করত। এই সময় ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ খুব সীমিত ছিল, ফলে শ্রেণীভেদ গড়ে ওঠেনি।
দ্বিতীয় ধাপ (শ্রেণীর উদ্ভব ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ): বাণিজ্যিক কৃষি, নগদ ফসল উৎপাদন, এবং বাইরের ব্যবসায়ীদের আগমনের ফলে ব্যক্তিগত জমি দখল ও সম্পদ সঞ্চয়ের মাধ্যমে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। উপনিবেশবাদী প্রশাসন এবং পরবর্তীতে আধুনিক রাষ্ট্র ভূমি জরিপ, কর ব্যবস্থা ও আইনি মালিকানা নীতি চালু করে, যা সমষ্টিগত মালিকানা ভেঙে দেয়। ফলে কিছু ব্যক্তি বা পরিবার বেশি সম্পদ ও ক্ষমতা পায়, অন্যরা বঞ্চিত হয়। এভাবেই শ্রেণীভেদ আদিবাসী সমাজে প্রবেশ করে।
তৃতীয় ধাপ (পিতৃতন্ত্রের অনুপ্রবেশ): বাইরের ধর্মীয় প্রভাব, পুরুষপ্রধান রাষ্ট্রীয় কাঠামো, এবং উপনিবেশ ও পরবর্তী আমলের প্রশাসনিক নেতৃত্ব পুরুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে। নারীর ভূমিকা সীমিত করে দেওয়া হয় শিক্ষা, বাজার ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণে। উত্তরাধিকার প্রথা ও নেতৃত্ব নির্বাচনে পুরুষকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে পূর্বের সমতাভিত্তিক বা মাতৃতান্ত্রিক ধারা ভেঙে গিয়ে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ় হয়, যা শ্রেণীভেদের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে আদিবাসী সমাজের রূপান্তর ঘটায়।
তবে সমাজ বিবর্তনের ধারায় শ্রেণী ও পিতৃতন্ত্র শেষ কথা নয়। পুঁজিবাদ উত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন ইউটোপিয়া নয়, বাস্তব ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রও শেষ কথা নয়। সমাজ সাম্যবাদের দিকেই এগুচ্ছে। যারা সাম্যবাদী রাজনীতি বুঝতে চান, আদিবাসীদের আদি সাম্যবাদী সমাজের ইতিহাস ও মূল্যবোধ থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে।